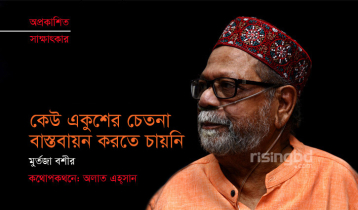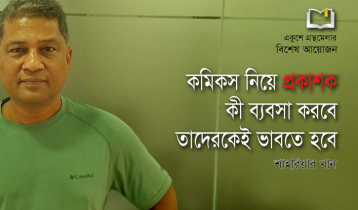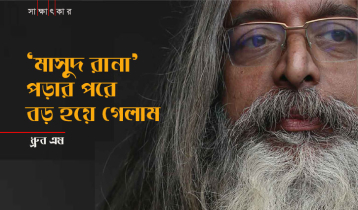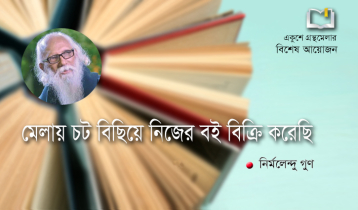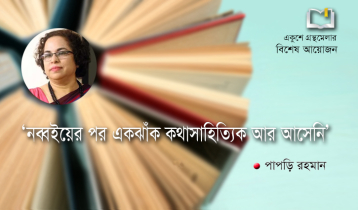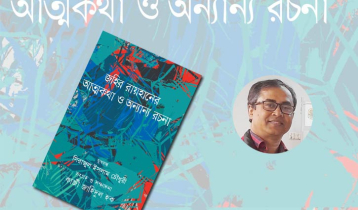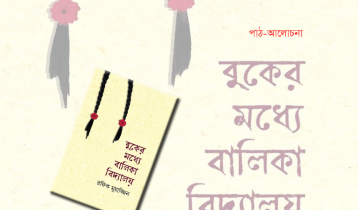একচক্ষু হরিণীরা: অষ্টম পর্ব
রাসেল রায়হান || রাইজিংবিডি.কম

ফোন বাজছে। সেই সাথে ফজরের আজানও ভেসে আসছে। আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম...
লাফ দিয়ে উঠলাম। বিকেলের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এখন ফজর হয়ে গেছে! খাইছে!
দীর্ঘক্ষণ ধরে রিং বাজছে মনে হয়। নইলে এত ভোরে ফোনের রিং টের পাওয়ার কথা না। ইনসমনিয়া আছে আমার। দশটার সময় শুয়ে পড়লেও ঘুম আসতে আসতে তিনটা-চারটা বাজে। তবে একবার ঘুমিয়ে পড়লে কেউ হাতি দিয়ে টেনেও ওঠাতে পারে না। জহুরুল হক হলের চারশ দুই নম্বর রুমে যখন আমি থাকি, বন্ধুরা একদিন ঘুমের মধ্যে আমায় ছাদে রেখে এসেছিল। টেরই পাইনি। পরদিন সাড়ে দশটায় কড়া রোদে ঘুম ভেঙে যায়। তাকিয়ে দেখি ছাদে শুয়ে আছি, উঁচু রেলিংয়ের পাশে।
আমার ঘরে চার-চারটা অ্যালার্ম ঘড়ি। কখনো সকাল সকাল কোথাও যাওয়ার থাকলে সবগুলিতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখি। একেটা একেক জায়গায়। তার উপরে মোবাইলের টোন।
এই ঘুমের জন্য আমি দু জায়গায় ভর্তিপরীক্ষা দিতে পারিনি, যার মধ্যে মেডিকেল একটা। মেডিকেলে ভর্তির পরীক্ষা ছিল সকাল নয়টায়, ঘুম ভেঙে দেখি সাড়ে এগারোটা বাজে। অন্যটা সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। শুক্রবার সকালে পরীক্ষা। ওখানকারই হলে এক বড় ভাইয়ের রুমে উঠেছিলাম। ঘুম ভেঙে দেখি আমায় তালা দিয়ে রেখে সে জুমা পড়তে চলে গেছে।
সেখানে মাত্র একবার টোনে আমার ঘুম ভাঙার কথা না। কিন্তু এত ভোরে কে ফোন দিল? চেনা কারও দেওয়ার কথা না। সবাই আমার ব্যাপারে জানে। আম্মা-আব্বার কাছে আমার নম্বর নেই।
এত ভোরে ফোন মানে অবশ্যই কোনো দুঃসংবাদ। ফোনটা অনেকক্ষণ চোখের সামনে রাখার পর টের পেলাম, আননোন নম্বর থেকে ফোন। তার মানে নিশ্চয়ই মুনিয়া। এমন অদ্ভুত সব সময়ে একমাত্র তার পক্ষেই আননোন নম্বর থেকে ফোন দেওয়া সম্ভব। একেকবার একেক নম্বর থেকে ফোন দেয় সে। তার জন্মই হয়েছে আমায় জ্বালিয়ে মারার জন্য।
প্রথম প্রথম মুনিয়ার ফোন এলে কথা শেষ করেই আগে ব্লক লিস্টে ফেলে রাখতাম। এক সময় ব্লক লিস্ট ভরে গেল। পরে নম্বর সেভ করে রাখতে লাগলাম। একবার ফোন এলে সেটা মুনিয়া ১, পরেরবার মুনিয়া ২, তারপর মুনিয়া ৩- এভাবে সেভ করি। সেভ করা নম্বর থেকে মুনিয়ার ফোন এলে আর ধরি না। মুনিয়াও মোটামুটি রবার্ট ব্রুসের ধৈর্য নিয়ে জন্মেছে। একের পর এক ফোন দিয়ে যায়। এ পর্যন্ত সেভ হওয়া তার লাস্ট নম্বরটি হলো মুনিয়া ৫২।
মুনিয়া আমার ছাত্রী ছিল। তখন পলিটিক্যাল সায়েন্সে পড়ি, ফাইনাল ইয়ার। ঋণটিন করে চলি। বাড়ির সাথে যোগাযোগ নেই কোনো। দিনরাত প্রুফ দেখি। লিখে টাকা আসে না তেমন। তিন-চারমাস পর একসাথে সব বিল তুললে হয়তো এক মাস চলে যায়। সেই বিল বাড়িতে পাঠিয়ে দিই আমার কোনো অ্যাড্রেস না দিয়েই। আব্বার ওষুধ খরচ উঠে যাওয়ার কথা ওতে।
এ অবস্থায় একজন একটা টিউশনির খোঁজ দিল। ছাত্রী। ভর্তিপরীক্ষা দেবে। আমায় সপ্তাহে তিনদিন বাংলা পড়াতে হবে। বিনা বাক্যে রাজি হয়ে গেলাম।
সেই বিনা বাক্যের ছাত্রী মুনিয়া। বাবার গার্মেন্টস ব্যবসা। বনানীতে বড় ডুপ্লেক্স বাড়ি। তিনতলা বাড়িতেও লিফট। মুনিয়ার বৃদ্ধ দাদু এই লিফটে ওঠানামা করেন। বিকেলে হুইল চেয়ারে করে লনে বসে বসে পোষা খরগোশগুলিকে গাজর খাওয়ান।
মুনিয়াদেরটাই আমার দেখা প্রথম ডুপ্লেক্স বাড়ি। এর আগে আমি জানতাম না, ঘরের ভেতর থেকে পেঁচিয়ে উঠে যাওয়া সিঁড়িঅলা এসব বাড়িকে ডুপ্লেক্স বলা হয়। সে হিসেবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাঠের যে দোতলা ঘরটিতে আমি শৈশব কাটিয়েছি, সেটিও আসলে ডুপ্লেক্স বাড়িই।
মুনিয়াকে পড়াতাম আর তাকিয়ে তাকিয়ে সবুজ লনে এলেমেলো ছুটে চলা শাদা আর বাদামী খরগোশগুলি দেখতাম। মুনিয়ার দাদুর বাড়িয়ে দেওয়া গাজরগুলো মুখে নিয়েই তারা দূরে ছুটে যেত। তীব্র ইচ্ছে হতো সবুজ লনে একবেলা শুয়ে থাকার। খরগোশগুলিকে গাজর খাওয়াতেও ইচ্ছে হতো। কোনোটাই হয়নি।
সর্বসাকুল্যে মুনিয়াকে পড়িয়েছি তিনদিন। তৃতীয়দিন পড়িয়ে এসেছি, এরপরেই শুনি আর পড়াতে যেতে হবে না। মুনিয়ার মা ফোন করেছিলেন। পরে যার মাধ্যমে টিউশনিটা পেয়েছিলাম, তার কাছে মুনিয়ার বাবা ৩০০০ টাকা পাঠিয়ে দেন। টাকাটা ফেরত দিয়েছিলাম আমি।
টিউশনিটা চলে যাওয়ার একমাত্র কারণ মুনিয়াই ছিল। পড়ানো তৃতীয় দিনেই মুনিয়া আমার হাতে একটা ছোট্ট চিরকূট ধরিয়ে দিয়ে ধীরকণ্ঠে বলেছিল, বাড়িতে গিয়ে খুলবেন। আমি সেখানেই খুলেছিলাম। সেটা আমার ভুল ছিল হয়তো। খোলার সময়ে দেখেছিলাম, মুনিয়ার গাল ধীরে ধীরে রক্তিম বর্ণ ধারণ করছে, পেকে ফেটে যাওয়া তরমুজের ভেতরটার মতো। কিংবা একুশ বছর বয়সে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দেখা সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটির মতন।
হালকা নীল কাগজে লেখা ছিল, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে খারাপ ভাবছেন। আমি খারাপই। কিন্তু এই খারাপ মেয়েটা আপনাকে ভালোবাসে।
আমি শুধু মুনিয়াকে বলেছিলাম, মনে রেখো, তুমি আমার ছাত্রী। আর কখনো এসব লিখবে না। মুনিয়া আস্তে মাথা ঝাঁকাল, সামান্য।
সেদিন আর পড়ানো হয়নি। পরদিন আসব বলে উঠে চলে আসি।
বহুবার অর্ধনগ্ন অচেনা একটি মেয়েকে স্বপ্নে দেখে ঘুম ভেঙেছে আমার। জিন্স-টিশার্ট পরা একটি মেয়ে শুয়ে আছে। তার ঘুমের মধ্যেই টিশার্ট খুলে ফেলি আমি। অন্তর্বাস খুলে বাঁপাশের বুকের উপর কান পেতে স্পষ্ট হৃদপিণ্ডের শব্দ শুনি। তারপর জিন্সের বোতামে হাত দিই।... আর তখন ঘুম ভেঙে যায়। এরপর আবার ঘুমানোর চেষ্টা করি বার বার, স্বপ্নটা পুরো দেখব বলে। হয় না। চোখ বুজে মটকা মেরে পড়ে থাকি।
সুতরাং আমি যে খুব চরিত্রবান, তা মোটেই নয়। এমনকি আমি ব্রথেলেও গেছি দুবার। সানন্দে সেটা স্বীকারও করি। আহির ছাড়া আর কারো কাছে নিজেকে সাধুসন্ত প্রমাণের স্পর্ধা কিংবা আগ্রহ, কোনোটাই নেই আমার। ছিল না কখনো। কিন্তু মুনিয়ার সাথে অমন ভারিক্কি ভাব দেখানোর একমাত্র কারণ ছিল, টিউশনিটা হারানোর ভয় পাচ্ছিলাম। এবং সেটাই ঘটল। বাসায় আসার পরপরই মুনিয়ার মায়ের ফোন পাই। আপাতত পড়াতে যেতে বারণ করেছেন। পরে আবার ফোন করবেন। ওনার বলার ভঙ্গিতেই আমি বুঝে গেলাম, আপাতত মানে আসলে সবসময়ের জন্যই।
পরদিনই মুনিয়ার ফোন পাই আমি। হ্যালো, আমি মুনিয়া।
আমি চুপ করে থাকলাম। ওপাশ থেকে আবার ভেসে এলো, হ্যালো, স্যার, আমি মুনিয়া।
আমি বললাম, বলেন।
স্যার, আমায় আপনি আপনি করে বলছেন কেন? চিনতে পারেননি? আমি মুনিয়া। বনানীতে আপনি যাকে পড়াতে আসতেন।
হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি। কিন্তু আপনাকে তো আর পড়ানো হবে না আমার। আপনি এখন আর আমার স্টুডেন্ট না।
মুনিয়া আমার কথা গায়ে লাগাল বলে মনে হলো না। সে বলল, স্যার, আপনি কিন্তু আমার জবাব দেননি।
অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, কিসের জবাব?
চিঠির।
কোন চিঠির?
আরে, আপনি ভুলে যাওয়ার ভান করছেন কেন? আপনি মোটেই কালকের চিঠির কথা ভুলে যাননি।
আমি থেমে থেমে বললাম, দেখো মুনিয়া, ওর জবাব আমি কালই দিয়েছি। আমি তোমার টিচার।
যেন জিতে গেছে এমন ভঙ্গিতে মুনিয়া বলল, সে তো গতকাল পর্যন্ত ছিলেন। এখন তো আপনি আর আমার টিচার না। আমিও আর আপনার স্টুডেন্ট না। এখন তো ওসব বলাই যায়।
আচমকা একটি বিষয় উঁকি দিয়ে গেল আমার মনে। এই টিউশনি চলে যাওয়ার পেছনে মুনিয়ার চাল নেই তো? সে ইচ্ছে করেই আমায় তাড়িয়েছে? যাতে আমি আর তার শিক্ষক না থাকি? আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। নিজের মাকে সে আমার সম্পর্কে কী বলেছে আল্লাহ জানেন। বুকে হাত-টাত দিয়েছি, এমন কিছু বলেনি তো? নাহ, এসব বলার কথা না। এটা বললে মুনিয়ার বাবা আমায় ছেড়ে দেবেন না। প্রথম দিন তাকে দেখেছিলাম আমি। তার ব্যক্তিত্ব, কথা বলার ভঙ্গি, চলন, সবকিছু বলে দেয় যে তিনি অল্পে ছেড়ে দেওয়ার মানুষ না। কিন্তু কী বলেছে সে?
আমি বললাম, মুনিয়া, তুমি আমার সম্পর্কে বাসায় কী বলেছ?
যা-ই বলি, আপনি এখন আর আমার টিচার নন। এখন আপনি আমায় ভালোবাসেন আর না বাসেন, আমি ঠিকই আপনাকে ভালোবাসতে পারব। অন্তত আপনি আর আমায় বারণ করার অধিকার রাখেন না। আর মাত্র তিনদিন পড়িয়ে খুব টিচার সাজবেন না। শোনেন, আপনি তিনদিন আমায় পড়িয়েছেন, আমি যখন মেডিকেলে ভর্তি হব, আপনাকে তিনদিন পড়িয়ে দেবো। শোধবোধ। আমি তো চোখের ডাক্তার হব, আপনাকে শিখিয়ে দেবো চোখের অপারেশন কীভাবে করে, কী কাটতে হয়-না হয়, সব। শোধবোধ।
আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। তারচেয়ে বেশি চমকে উঠলাম। সব রেখে মুনিয়া চোখের কথাই বলল কেন? আমি ‘রাখছি’ বলে ফোন কেটে দিলাম। ‘মুনিয়া ২’ লিখে সেভ করে নম্বরটা ব্লাকলিস্টে রেখে দিরাম। ‘মুনিয়া ১’ দিয়ে সেভ করা ছিল মুনিয়ার মায়ের নম্বর। সেটাও ব্লক করলাম। এরপর দীর্ঘ চার বছর ধরে মুনিয়া ফোন দিয়ে যাচ্ছে। একবার দেখা করতে চায়। সাধারণত মুনিয়ার কণ্ঠ শুনলেই আমি ফোন কেটে দিই। এর মধ্যেও যা দুয়েকবার কথা হয়েছে, সামান্য। শুধু জানি, মুনিয়া এখন সলিমুল্লাহ মেডিকেলে পড়ছে।
একদিন মুনিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি সব রেখে আমার চোখের কথা কেন বলেছিলে?
মুনিয়া অবাক হয়ে বলেছিল, কেন, চোখে সমস্যা কী। তারপর জোরে জোরে হাসতে লাগল অনেকক্ষণ।
আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, চোখের কথা কেন বললে, বলো।
মুনিয়া টেনে টেনে সুর করে বলল, বলব, আগে দেখা করেন।
আমার এখনো জানা হয়নি, মুনিয়া সব রেখে আমার চোখের কথা কেন বলল? আই স্পেশালিস্ট হবে মুনিয়া, এটা একটা কারণ হতে পারে অবশ্য।
দীর্ঘ চারবছর বাদে মুনিয়ার সাথে দেখা করার আগ্রহ হচ্ছে। আননোন নম্বর থেকে ফোন বেজেই যাচ্ছে। নির্ঘাৎ মুনিয়াই হবে। ফোন রিসিভ করে বললাম, আচ্ছা, তুমি সব রেখে চোখের ডাক্তার কেন হলে, বলো তো?
ওপাশ থেকে ভেসে আসলো আহিরের পরিচিত কণ্ঠ, কী বলছ এসব? আমি আবার চোখের ডাক্তার কীভাবে হলাম?
আমি গলা খাকারি দিয়ে বললাম, আহির নাকি? কী ব্যাপার? এত ভোরে কেউ কাউকে ফোন দেয়?
আহির বলল, আজ আমায় দেখতে আসছে। তোমার সাথে খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছিল।
তেরো
আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম, বাবাকে নিয়ে। সেই কবিতাটা সত্যিকার অর্থে আমার মাকে নিয়ে লেখা। কিন্তু সাহিত্যে সত্যিকারের জিনিস অবিকল লিখলে যত রসই দেওয়া হোক, যতটা নন্দনের সমুদ্রই বইয়ে দেওয়া হোক, পত্রিকার রিপোর্ট মনে হয়। যেকোনো সাহিত্যেই সবসময়ে কিছু মিথ্যে ঢোকাতে হয়, স্বর্ণালঙ্কারের খাদের মতন। খাদটুকু না থাকলে অলঙ্কার মজবুত হয় না। এই কথাগুলো কি আগেই সাহিত্যের রথী-মহারথীরা কেউ বলে ফেলেছে? বললে বলুক। বরং কবিতাটা পড়া যাক আগে।
১.
মাছের লেজের ঢঙে, মাছির ডানার ঢঙে জেগে উঠতেন আমার বাবা। তারপর ছুটতেন বাজারে। রাতে যখন ফিরে আসতেন মাছ ও মাছির গন্ধ নিয়ে, আমি ভাবতাম, আহা, একদা কি চন্দনের ঘ্রাণ নিয়ে আসতে পারেন না? (তখন মোটেই জানা ছিল না, সেসব নিয়ম অনেক আগে উঠে গেছে, আজকাল শুধু মৃত্যু এই গন্ধ নিয়ে আসে)। আজ রাতে যখন বাবার শরীর ভর্তি চন্দনের ঘ্রাণ, ভাবছি, মাছ ও মাছির গন্ধ আরও বেশি ভালো ছিল!
২.
আমি যখন ক্লাস ওয়ানে পড়ি, ফিস চাইতে গেলে বাবা আমার দিকে ম্রিয়মান ভঙ্গিতে তাকিয়ে ছিলেন, যেন তার মনে পড়ে গেছে গত রাতের কথা, যখন আমি মোমের আলোয় চেঁচিয়ে পড়ছিলাম, ‘ফিস মানে মাছ, ফিস মানে মাছ...।’
তিনি মাছ কুটছিলেন। সেই মুহূর্তে আমার দিকে মনোযোগ দেওয়ার ফলে তার একটি আঙুল ছিন্ন হয়ে যায়। যেহেতু ফিস দেওয়া হচ্ছেই না, কিছু অ্যাডভেঞ্চার করা যাক ভেবে আমি সেই আঙুল রঙিন পেপারে মুড়ে স্কুলে জমা দিয়ে দিলাম।...এইভাবে দশম শ্রেণি পর্যন্ত দশ ক্লাসে দশটি আঙুল জমা পড়ে স্কুলে! স্কুল ছাড়ার আগে ফিজিক্স-টিচার দেখলাম শল্যচিকিৎসকের ভূমিকায় নেমে গিয়ে কাগজে মুড়িয়ে রাখা পুরাতন দশটি আঙুল আমার দুহাতে লাগিয়ে দিলেন। নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, আমার সন্তানকে বিশ ক্লাস পড়াতে পারব। সেও নিশ্চয়ই তার সন্তানকে পড়াবে ত্রিশ-ত্রিশটি ক্লাস...
কবিতার প্রথম অংশটা ব্যাখ্যা করা যাক। এই কবিতায় যে চন্দনের ঘ্রাণের কথা বলা হয়েছে সেটা আসলে হিন্দুয়ানী রীতি। মৃত্যুর পর শ্মশানে পোড়ানোর সময় চন্দন কাঠ ব্যবহারের রেওয়াজ, যদিও এখন চন্দন কাঠ অতটা সহজলভ্য এবং সস্তা না হওয়ায় সে রীতিও উঠে গেছে। যা-ই হোক, আমার বাবাকে মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই কবর দেওয়া হবে। চন্দনের ঘ্রাণ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ভাগ্যিস আজ পর্যন্ত কোনো পাঠক এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেনি।
এবার দ্বিতীয় অংশে আসা যাক। এক সিনিয়র কবি আমায় বলেছিলেন কবিতাটা পড়ে নাকি সারারাত ঘুমাতে পারেননি। তিনি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, আমার বাবা কী করেন। তিনি সত্যিই মাছের ব্যবসা করেন কি না। আমি হেসেছিলাম। বলতে ইচ্ছে হয়নি, আমার বাবা অন্ধ। তিনি একটি পান সিগারেটের দোকান চালান, দূর এক মফস্বলে। এই কবিতার সাথে তার দূর-দূরান্তেরও কোনো সম্পর্ক নেই। বরং আমার মায়ের একটি স্মৃতি আমার মনে পড়ে। বাবার পান-সিগারেটের দোকান থেকে আমাদের ভালোই চলে যাচ্ছিল। এমনিতেই চালু দোকান। বাবার অন্ধত্ব এবং ভালো ব্যবহার, এই দুইটা জিনিসই দোকানটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। তাও মায়ের টাকার প্রয়োজন ছিল। বড় হয়ে বুঝতে পেরেছি বাবার চোখের অপারেশনের জন্য মা টাকা জমাচ্ছিলেন। রোজ খুব ভোরে মা পাইকারী বাজার থেকে মাছ কিনে আনতেন। সেই মাছ আঁইশ ছাড়িয়ে, কেটেকুটে আমায় দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে দিতেন। ভাগা বিক্রি করতাম। একবেলা মাছ বিক্রি করে এসে দুপুরের পরে স্কুলে যাই আমি। টিফিনের পরের পিরিয়ডগুলি ধরি। স্কুলের স্যাররা এটা মেনে নিয়ে ছিলেন।
এক ঝুম বর্ষায় আমার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম থেকে উঠে রান্নাঘরে যাই। দেখি মা একপাশে ইলিশ মাছের টুকরো রেখে উঁবু হয়ে কী যেন করছেন। অন্য পাশে প্রমাণ সাইজের বটি। কাছে গিয়ে দেখি মা হাত বাঁধছেন। মাটিতে তাজা রক্ত। হাত কেটে গেছে। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে মা আমার দিকে তাকান। তাকিয়ে করুণ একটা হাসি দেন। সেই রক্ত এবং করুণ হাসির দৃশ্য অনেকদিন গেঁথে ছিল আমার মনে। এই কবিতা ছিল সেই দৃশ্যের উপশম। লিখতে গিয়ে দেখি কীভাবে জানি মায়ের জায়গায় বাবা হয়ে গিয়েছে। সম্ভবত আমার অবচেতন বলছিল, এখানে মা হলে লেখাটার গ্রহণযোগ্যতা কিংবা বিশ্বাসযোগ্যতা থাকবে না। অনেক সত্যিকারের জিনিসই সাহিত্য স্পর্শ করতে পারে না। যেমন মাকে নিয়ে লেখা একটা কবিতা ছাপা হওয়ার পরে আবার যখন পড়ি আমি, বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল কবিতাটি আসলে আমার মাকে নিয়ে লেখা না, লেখা আহিরকে নিয়ে। আচ্ছা, কখনো কি মা আর প্রেমিকা গুলিয়ে যেতে পারে?
আহিরই কি আমার প্রেমিকা? সেটা বলা মোটেই ন্যায়সঙ্গত হবে না। আহির আমাকে সহজভাবে দেখে। আমার সাথে অনেককিছু শেয়ার করে। দুয়েকবার হাত ধরেছে। ব্যস, ওটুকুই। এর মানে প্রেম- কোনো বোকাও এই দাবি করবে না। যখন সে বারো বছর বয়সে তার এক ফুপার দ্বারা শারীরিকভাবে ব্যবহৃত হওয়ার কথা বলছিল, তখন মনে হয়েছিল আমার কাছেও সে আসলে আশ্রয় চায়। মানসিক একধরনের নিরাপত্তা চায়। একটা মেয়ে তার সারাজীবনে কত কত স্মৃতি নিজের ভিতরে কবর দিয়ে রাখে! বেশিরভাগ মেয়েরই বলার মতো কেউ থাকে না। বাবাকে কিছু বলা যায় না, সম্পর্কের গঠনটাই অমন। স্বামীকে তো বলা যায়ই না। সংসার ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সাতানব্বই ভাগ। স্বামী ভদ্রলোক যতই খোলা এবং সহজ মানসিকতার বলে নিজেকে প্রমাণিত করুক, স্বামী আসলে স্বামীই। সে স্ত্রীর প্রতি অধিকার খাটাতে চায়। নিজেকে খোলা মানসিকতার বলে স্ত্রীর কাছে তার ভাবমূর্তিটি ঈশ্বরসুলভ করতে চায়। ওর মূলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খোলা কিছু থাকে না। সেটা সরল বিশ্বাসে বলা বেশিরভাগ মেয়েই টের পায়।
বন্ধুকে বলা যায় না সব।
আচ্ছা, মাকেও কি বলা যায়?
তাহলে বলা যায় কাকে? একটা মেয়ে সারাজীবন এই মানুষটাকে খুঁজে বেড়ায়। এই মানুষগুলিই দেখতে তার প্রেমিকের মতো হয়। বিবাহিত মেয়েরা বলার মানুষ খুঁজে পেতেই বেশিরভাগ পরকীয়ায় লিপ্ত হয়। আমি কি আহিরের সেই প্রেমিকের মতো দেখতে মানুষটি? আহির তো অবলীলায় তার প্রেমপ্রার্থীদের গল্প বলে আমার কাছে। এমনকি গত দুবছর ধরে তার পেছনে পেছনে ঘোরা যুবকটিকেও দেখিয়েছে আমায় নির্দ্বিধায়। সাদাসিদা মুখের এক যুবক। সানগ্লাস পরে প্রায়ই বসে থাকে আহিরের অফিসের কাছের চায়ের দোকানে। দুয়েকবার আহিরকে বাসায় পৌঁছে দিতে গিয়েও দেখেছি তাকে। কাজকর্ম কিছু করে না বোধ হয়। নইলে সারাক্ষণ পিছু নেয় কীভাবে! পিছু নেওয়া ছাড়া আর কিছু করেও না আবার। একবার একটা প্রেমপত্র দিয়েছিল আহিরকে। আহির সেটা তার সামনেই পড়ে ফেরত দেয়। বলে এসব আমাকে আর কখনো লিখবেন না। যুবকটি অতিরিক্ত ভদ্র বোধ হয়। আর কখনো লেখেনি কিছু। কিছু বলার চেষ্টাও করেনি।
আমি একবার কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম যুবকটির সাথে। কাটিয়ে গেছে। খোঁজ নিয়েছি পরে। আশফাক নাম। বাবা-মায়ের এক ছেলে। এসএসসি পর্যন্ত পড়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। বাবার ভালোই টাকাপয়সা। শ্যাওড়াপাড়াতেই পাঁচতলা একটা বাড়ি আছে।
ঠাট্টা করে একবার আহিরকে বলেছিলাম, তুমি রাজি হয়ে যাও না কেন? পড়াশোনা নেই তো কী? বেচারা তোমাকে ভালোবাসে।
আহির আহত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। ভেজা পল্লব। তারপর আর এই প্রসঙ্গ তুলিনি কখনো। কোন পাগলে তুলবে!
যে প্রসঙ্গে শুরু করেছিলাম, ফেরত আসি। সাহিত্যে সত্যিকারের জিনিস লেখা যায় না কখনো। এমনকি কাকে নিয়ে লিখেছে সেটা লেখক নিজেই অনেকসময় বিভ্রান্ত হয়ে যায় বলে আমার ধারণা। আমি যেমন নূরীর সাথে ঢাকায় দেখা হওয়ার পর কোন কবিতাটা আহিরকে নিয়ে লেখা, কোনটা নূরীকে নিয়ে, গুলিয়ে ফেলি। মাঝে মাঝে মনে হয় এসব আসলে আমার অন্ধ বাবাকে নিয়েই লেখা। আবার মনে হয়, শুধুই আমার মাকে নিয়ে লেখা। একদিন তিনি এইসব কবিতা পড়বেন। পড়ে বুঝতে পারবেন, আমি যতটাই স্বার্থপর আর ভীতু হই, সত্যিকার অর্থে আমি তাকে কতটা ভালোবাসি। একদিন ‘১৯৭০’ নামের কবিতাটা পড়ে বাবা বুঝতে পারবেন, শুধু তাকে আমি কতটা ভালোবাসি। নাকি ওটা মাকে নিয়ে লেখা...
একদিন দুজনেই আমায় ক্ষমা করে দেবেন নিশ্চয়ই। কোনো একদিন।
রাইজিংবিডি/ঢাকা/৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭/তারা
রাইজিংবিডি.কম
আরো পড়ুন