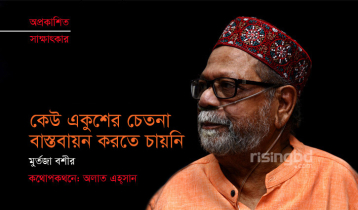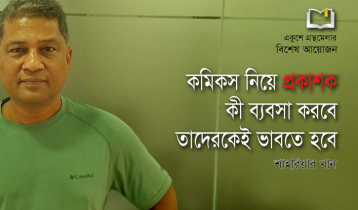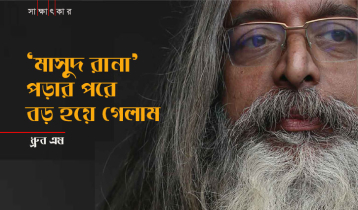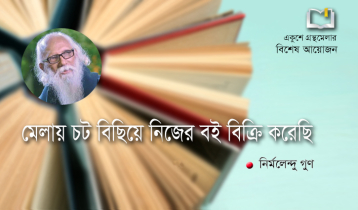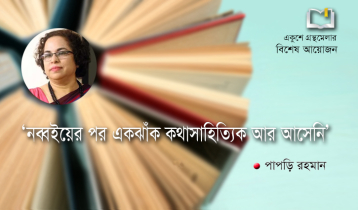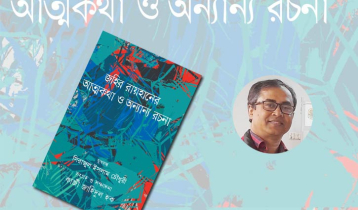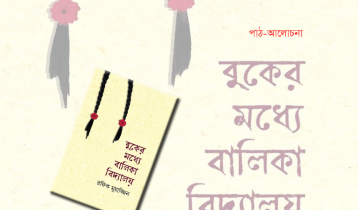মনিরা কায়েসের গল্পপাঠ: অন্ধ কুলঙ্গির টীকাভাষ্য
কুমার দীপ || রাইজিংবিডি.কম

মানুষের আবেগ ও অনুভূতির সৃজনশীল প্রকাশই হলো সাহিত্য। সত্যম্, জ্ঞানম্, অনন্তম্ অর্থাৎ আমি আছি, আমি জানি এবং আমি প্রকাশ করি। উপনিষদ অনুসারে ব্রহ্মস্বরূপের এই যে তিনটি ভাগ, এর মধ্যে ‘আমি প্রকাশ করি’ গুণটি একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মানুষের এই প্রকাশগুণ বা প্রকাশের ক্ষমতা ও আকাঙ্ক্ষা থেকেই শিল্প-সাহিত্যের জন্ম। প্রকাশের এই ক্ষমতা ও আকাঙ্ক্ষা ব্যবহার করেই একজন শিল্পী বা সাহিত্যিক তাঁর শিল্প বা সাহিত্য উপস্থাপন করেন। তাঁর পছন্দ, প্রবণতা ও দক্ষতা অনুযায়ী উপস্থাপনের পদ্ধতি ও প্রকরণ ভিন্ন হয়ে থাকে। এবং এই গুণেই শিল্পী বা সাহিত্যিক স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন। বর্তমান বাংলা ছোটগল্পচর্চায় মনিরা কায়েস (১৯৬১) তেমনই একটি স্বতন্ত্র ও সম্ভ্রমযোগ্য নাম।
মনিরা কায়েসের কথা বাজার চলতি সাহিত্যের পাতায় প্রায় দেখাই যায় না। চলমান সাহিত্যমঞ্চের আসরে তাঁর নাম উচ্চারিত হয় না বললেই চলে। তিনি নিজেও বোধকরি এগুলো এড়িয়ে থাকেন। এড়িয়ে থেকেই রচনা করেন ভাষাচিত্রের স্বতন্ত্র ভুবন। ‘অন্ধ কুলঙ্গির টীকাভাষ্য’ গল্পগ্রন্থটি এই স্বতন্ত্র ভুবনের এক অনন্য সংযোজন। মাত্র ছয়টি গল্প নিয়ে একশো কুড়ি পাতার এই বইটির এক-একটি গল্প বেশ দীর্ঘ। একটি গল্পের ভেতরে মেলে অনেক গল্পের স্বাদ; কখনও কখনও উপন্যাসেরও গন্ধও। কিন্তু উপন্যাস নয়, আসলে একটি গল্প বলতে গিয়ে অনেক গল্প বলবার এই প্রবণতা জীবনের বহুরৈখিক ব্যঞ্জনা ধারণ করবার প্রয়াস বলেই মনে হয়। জীবনের কোনো গল্পই যে একটিমাত্র গল্প নয়, জীবনের কোনো পথই যে পূর্ব-নির্দেশিত সরল পথ নয়- কথাটি বারবার স্মরণ করিয়ে দেন লেখক। তাঁর চরিত্ররা একইসঙ্গে কাল ও কালাতীত হয়ে, দেশ ও দেশাতীত ঘুরে বেড়ান। অথবা বলা যায় লেখক তাঁর চরিত্রদের মাধ্যমে পাঠককে কালা থেকে কালাতীতে, ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিকে ঘুরিয়ে বেড়ান। অন্যভাবে বললে, মনিরা কায়েস তাঁর নিজস্ব প্রবণতা অনুসারে চরিত্রসমূহকে সঙ্গে নিয়ে পথ ও পথের দু’পাশের সবকিছু দেখতে দেখতে, বিবিধ অন্ধকারে নজর রাখেন, মানুষ ও মানবতার দেয়াল খুঁড়ে মানুষ যে অন্ধ কুলঙ্গিরাজ্য তৈরি করেছে, তা ঘুরে ঘুরে আমাদের দেখান। তাঁর অনন্য লিখনশৈলীর মাধ্যমে আমরা সেগুলো দেখি আর ভাবি। আমাদের ভেতরেও তৈরি হয় বিবিধ ক্ষত।
২.
বিখ্যাত রুশ কথাসাহিত্যিক ইভান বুনিনের প্রেম, সাহিত্য ও স্থিরতাহীন জীবনের একটি বিশেষ অংশ ‘হৃত হেমন্তের দীর্ঘশ্বাস’ গল্পের উপজীব্য। প্রসঙ্গক্রমে গল্পকার তুলে এনেছেন পুশকিন, ম্যাক্সিম গোর্কি, ইভান তুর্গেনেভ প্রমুখকেও। রাশিয়ান সাহিত্যের ঈষৎ সারাৎসার যেন ছুঁয়ে যেতে চেয়েছেন তিনি। বিশেষ করে বুনিনের একাধিক বিখ্যাত গল্পসার পাঠককে ছুঁয়ে যায়। এসে পড়ে পুশকিনের ‘মোৎসার্ট ও সালিয়ারি’ প্রসঙ্গ। লেখক সূক্ষ্ম রসবোধ আর অসামান্য কল্পনাশক্তির সৃজনশীলতা দিয়ে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন রাশিয়ান জীবনবোধ ও জীবনানুষঙ্গের বিশেষ উপাচারসমূহ।
ইভান বুনিন। যাঁর সম্পর্কে ম্যাক্সিম গোর্কি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘বুঝি না নিষ্প্রভ রুপোর মতো এমন অপূর্ব তার প্রতিভা তিনি শানিয়ে ছোরা করে যথাস্থানে বেঁধাচ্ছেন না কেন?’ কিন্তু বুনিনের জীবন, তাঁর কর্ম, সাহিত্য, প্রেম সবখানেই অস্থির, সিদ্ধান্তহীনতার আধার। তার জন্মের সময় কুল-জ্যোতিষী নাকি বলেছিলেন, ‘পাক খাওয়া কপাল, কোনও দিন এর সুখ চিরস্থায়ী হবে না।’ জ্যোতিষীর একথা শুনে বুনিনের ঠাকুরদা রেগে গেলেও, মা-ঠাকুমা নানা ‘ঝাড়ফুঁকের বিপদতাড়ন-মাদুলি’ কিংবা আঁতুড়ঘরে মাতা মেরির আইকন বসিয়েছিলেন। তা-সত্ত্বেও জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বাণী সত্যি করে তুলবার মিশনেই যেন বুনিন সবসময় লেগেছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা অসমাপ্ত রেখে ভবঘুরে জীবন কাটাতে থাকা বুনিন জীবিকার ক্ষেত্রেও ছন্নছাড়া। কোথাও বেশিদিন মন বসে না তাঁর। কোনোখানেই থিতু হতে না পারা এই মানুষটির জীবনে প্রেম এসেছে একাধিকবার, কিন্তু সে-ও বোধহয় ‘পাক খাওয়া’ কপালের মতো, ক্ষণজীবী। না কি বংশগতভাবেই বুনিন এই প্রেমহীন প্রেমের উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন? বুনিনের একজন প্রেমিকার বয়ানে ‘হৃত হেমন্তের দীর্ঘশ্বাস’-এর যে ক্ষরণ গল্পে প্রতিফলিত হয়, তাতে আমরাও জারিত হই। বুনিনকে খুব গভীরভাবে ভালোবাসা এই প্রেমিকাও বুনিনের খেয়ালি প্রেমের বলী হয়েছে।
কষ্ট ও দীর্ঘশ্বাসে জারিত হতে হতে বুনিনের জীবন থেকে অন্তর্হিত হওয়া এই নারীর তীব্র হাহাকারের বেদনা আমাদেরও ছুঁয়ে যায়। আমরা অনুভব করি, নারী-পুরুষের একেবারে ভেতরে, যেখানকার কোনো দৃশ্য বাইরের থেকে দেখা যায় না; তারই টীকাভাষ্য রচনার প্রয়াস পেয়েছেন গল্পকার মনিরা কায়েস।
৩.
‘মিরার ভজন অথবা...’ গল্পটিও নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভেতরের রহস্য উন্মোচনের প্রয়াস। তবে আগেরটিতে নারী পরাভূত, এটিতে পুরুষ। এখানেও মনিরা কায়েস তাঁর সহজাত স্বতন্ত্র ভঙ্গিমায় গল্প বুনে বুনে এগিয়ে যান। এই বুনন কোনো কাহিনির সরল বয়ান নয়, একটি গল্পের ভেতরে অজস্র গল্প ও গল্পানুষঙ্গের বহুরৈখিক সেলাইকর্ম যেন। ‘মিরার ভজন অথবা...’ গল্পটি সাইফুল নামের পুরুষ মানুষটির প্রকাশ-অযোগ্য হাহাকারের অনুরণন। সেই হিসেবে সাইফুল কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু সাইফুল নয়, এমনকি লেখকও নন; সাইফুলের বন্ধু মাহবুবকে সামনে রেখেই এই গল্পের টীকাভাষ্যসমূহ পাঠকের নিকট তুলে ধরেছেন মনিরা কায়েস। গল্পকারের কথনরীতির স্বাতন্ত্র্যেরই প্রতিনিধিত্ব করে এটি। স্ত্রী মিরা ছেড়ে যাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় মাহবুবকে দেখি সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে রাজশাহীর উপশহরে দুই বিঘা জমি কিনে সেখানে ঘানি স্থাপন করে ‘মল্লিকা খাঁটি সরিষার তেল’-এর ব্যবসার তোড়জোড় শুরু করে। ব্যবসায় সাফল্যের জন্য বিজ্ঞাপন তৈরি করতে পেশাদার নির্মাতা ও মডেলের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু ব্যবসা শুরু করতে না করতেই কী খেয়ালে সেটা বাদ দেয়। ঘানি তুলে দিয়ে সেখানে গড়ে তোলে গরু মোটাতাজাকরণ ফার্ম। গরুর মাংস ও দুধের ব্যবসায় যখন লাভের সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত, তখনই রহস্যময়ভাবে ছেড়ে দেয় গরুর ব্যবসাও। এ-খবর জানতে পেরে বন্ধু মাহবুবের মনে হয়, সাইফুলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। না-হলে সুন্দর একটা সরকারি চাকরি ছেড়ে দিলো, বিরাট আয়োজন করে তেলের ব্যবসায় নেমে ছেড়ে দিলো, এরপর গরুর ফার্ম করেও তা লাঠে তুলে দিলো! এভাবে একের পর এক গোছানো টাকা নষ্ট করে যে, তার তো মাথা খারাপ হয়েছে বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় মাহবুব। কোনোদিন কোনো অনৈতিক কাজের সাথে জড়িত না-হওয়া, মদ পর্যন্ত না-ছোঁওয়া নিপাট ভদ্রলোক সাইফুলের মনের অবস্থা অনুমান করে আতঙ্কিত হয় মাহবুব। নামী কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে দিয়ে তার চিকিৎসার কথা ভাবে।
অফিস থেকে দুদিনের ছুটি নিয়ে রাজশাহীতে, সাইফুলের বাসায় পৌঁছানোর পরে সাইফুলের অবস্থা দেখে প্রথমে স্বাভাবিক মনে হলেও গভীর শীতের রাতে দীর্ঘ সময় ধরে বাথরুম থেকে সাইফুলের গোসলের শব্দ ভেসে আসতে থাকলে আবারও দুর্ভাবনা গ্রাস করে তাকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সাইফুলই তাকে ভাবনামুক্ত করে। জিজ্ঞাসা করার দরকার হয় না, নিজেই উন্মোচন করতে শুরু করে তার অস্বাভাবিক সব কর্মকাণ্ডের পেছনের রহস্যগুলো।
কী চায় সে? কুয়াশাপীড়িত ভোরে ঘোরগ্রস্ত পটভূমিতে ডুবে যেতে যেতে খড়কুটো জড়িয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা মানুষের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে দিশেহারা গলায় ফিসফিস করে সাইফুল জানায়- ‘দেখতে চাই, আমিও কিছু ফলাতে পারি কি না?’
গল্পের এই শেষবাক্যটি সাইফুলের হৃদয়ের অসীম হাহাকারের ব্যঞ্জনাময় অনুরণন। যে-সন্তান সাইফুল দিতে পারেনি, সেই সন্তান মিরা এখন পেয়েছে অন্যের নিকট থেকে। তার সন্তানের হাহাকার মিটেছে, কিন্তু সাইফুল? সামান্য বরইগাছে বরই এনে সে নিজের কাছেই যেন নিজের সান্ত্বনা দাঁড় করায়। কিছু একটা ফলাতে পারার সার্থকতায় আত্মতৃপ্ত হতে চায়। এটাও এক জীবন বটে।
এই গল্পটির প্রাণকেন্দ্রে অবশ্যই স্ত্রী-হারানো সাইফুলের অনিঃশেষ হাহাকার প্রতিস্থাপিত, তবে এর অতিরিক্ত আরও বেশকিছু বিষয় আমরা পেয়ে যাই। গল্পকার কেবল সাইফুল-মিরার গল্প বলেন না, বলেন মাহবুবের ঘরে-বাইরের গল্পও। উঠে আসে আশফাকের মতো রমণীমোহন বন্ধু, ঢাকা শহরের রাতের বিনোদন, নাগরিক জীবনের নানারকমের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার ভেতরের কথাও। ব্যবসা-বাণিজ্য-বিজ্ঞাপন এবং মুক্তবাজারের নানা অন্ধি-সন্ধিও ছুঁয়ে আসেন গল্পকার। মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ ও স্বাধীনতাবিরোধীদের কথাও বাদ থাকে না। প্রবল বায়ুদোষের কারণে সবসময় গোসল করতে চাওয়া কোনো এক হান্টুদাদার কথাও উঠে আসে, যে একদিন মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল ভেজা কাপড়ে। আরও কতো কী ! একটি গল্পের ভেতরে আরও একাধিক গল্প ও গল্পানুষঙ্গকে অবলীলায় ভরে দিয়ে গল্পকে বিবিধ ব্যঞ্জনায় ভরে তোলেন মনিরা।
৪.
নারীজীবনের অব্যক্ত দিনলিপি ‘ম্লান জ্যোৎস্নার ছাপচিত্র’ গল্পটি। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর ধরে বাঙালি নারী যে অর্ধ-নিয়ন্ত্রিত জীবন বয়ে বেড়ায়, তার ভেতরের সেই কথাগুলো, যেগুলো কেবল তাদের কাছেই জমা থাকে আনন্দ-বেদনায়, স্মৃতি-বিস্মৃতিতে- বাইরের জগতে, বিশেষত পুরুষের প্রচলিত পৃথিবীতে যার প্রায় প্রবেশাধিকার নেই; সেই কথাগুলো আমাদের কাছে পৌঁছে দেন গল্পকার মনিরা কায়েস। নাসিমা নামের মেয়েটির অনুভবে, বয়ানে, স্মৃতিক্ষরণে আমরা অন্ধ কুলঙ্গির কতিপয় টীকাভাষ্যের সন্ধান পাই।
নাসিমার মাধ্যমে যে-মানুষটির খবর এই গল্পের প্রধান আধেয় হয়ে ওঠেন- তিনি নাসিমার নানিমা। নানা বেঁচে থাকতেও যিনি অনেক দিন থেকে কোনো অলঙ্কার পরেন না, সাদা শাড়ি পরেন। বিরাট ধনী পরিবারের গৃহিণী, ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনি নিয়ে ভর-ভলন্ত সংসার, কোনোকিছুতেই কমতি নেই; তবু কিসের যেন অভাব, কিসের যেন হাহাকার তার ভেতরে কাজ করে, কোথায় যেন তাকে খুব বিষণ্ন ও একা মনে হয়। তাইতো তিলকাসুন্দরীর কাহিনি শোনাতে শোনাতে যখন তিনি চোখের জল ফেলেন, তখন নাসিমা বুঝতে পারে ‘এই জল তাঁর অন্তর্গত বেদনার স্রোত।’ তার মনে হয়, ‘তাহলে কাউকে ভালোবেসেছিলেন নানিমা?’ কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবে- শরীর-মন গড়ে ওঠার আগে মাত্র ন’বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল যার, তার তো কাউকে ভালোবাসার সুযোগ পাওয়ার কথা নয়। নাসিমাদের সঙ্গে পিকনিক করতে গিয়ে বিষণ্নতার চাদর বিছানো শেষ বিকেলে নানিমা যখন গান ধরেন ‘‘গাছের পাতা লড়ে চড়ে / মা কহ্যা মনে পড়ে / মাগো মা / কুন পাহাড়ে বিহা দিলি দেখতে প্যানু না...’, তখন তাঁর অন্তর্খননের আর্তি নাসিমাদের ভেতরেও ছুঁয়ে যায়। দুখনি নানির স্বামীর লাম্পট্যের বিচার করতে গিয়েও যখন আহত পশুর মতো ফিরে আসেন, তখন নাসিমার মতোই, সচেতন পাঠকের মনেও সন্দেহ ঘনিভূত হতে থাকে; কোনো অন্ধকারের গন্ধ অনুসন্ধান করতে থাকেন ভেতরে ভেতরে । কোন সেই অন্ধকার?
নাসিমার সাথে নানিমার কথোপকথনের সূত্র ধরে আমরাও একসময় সেই অন্ধকারের সন্ধান পেয়ে যাই। অনেক দিন আগে পথের জটিলতায় বাপের বাড়ি থেকে গভীর রাতে বাড়ি ফিরে স্বামীশূন্য বিছানা দেখে বুকটা ভারি হয়েছিল নানিমার। খিড়কির দরজাটা বাইরের থেকে বন্ধ দেখে খাঁ খাঁ বুকে নিজেকে প্রশ্ন করেন নানিমা- ‘আমি কি তারে ভালোবাসা দিই নাই, সেবাযত্ন করি নাই? কিসের অভাবে তাহলে পা রাখছেন খিড়কির ওপারে?’
নিজের পৃথিবীটাকে এভাবে টলমানরূপে আবিষ্কার করা নানিমা ভেতরে ভেতরে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে অনেক ভেবেচিন্তে পরের দিনই চরম এক সিদ্ধান্ত নেন। শরীর থেকে সমস্ত গয়নাগাটি খুলে ফেলে, রঙিন শাড়ি তুলে রেখে একখানা সাদা শাড়িতেই জীবন কাটানোর প্রত্যয় গ্রহণ করেন। মনে মনে বলেন ‘আজ থেকে জানলাম আমি বিধবা।’
স্বামী থাকতে, সংসারে সন্তান-সন্ততিসহ আরও অনেক মানুষ থাকতে, সধবার পোশাক পরিহারে নানিমার অবিশ্বাস্য এই দৃঢ়তা কেবল নাসিমাকে নয়, গল্পের পাঠককেও নাড়িয়ে দেয় তুমুল আলোড়নে। যে-সমাজে নারীর অধিকার ও কর্ম অধিাকংশক্ষেত্রেই পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেই সংসারের একজন হিসেবে নানিমার এমন সিদ্ধান্ত ও তার বাস্তবায়ন পুরুষশাসিত সমাজের গালে দুরন্ত এক চপেটাঘাত বৈকি।
নানিমার জীবন কাহিনি প্রধান বিষয় হলেও বরাবরের মতোই জীবনের আরও অনেক গলিঘুঁজির সন্ধান পাই এই গল্পেও। দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ভালোবাসা-স্নেহ প্রসঙ্গে এসে পড়েন রবীন্দ্রনাথ-মৃণালিনী, বঙ্গবন্ধু-রেণুও। বউদি কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর আগে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ঠাঁই না-পাওয়া স্ত্রী মৃণালিনী দেবীই একদিন অলঙ্কার বেচে দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের জন্য, কারাগারে থাকা বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে ছেলে-মেয়েদের সাধ-আহ্লাদ সামলাতে হিমসিম খেয়েছেন ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ( রেণু)। প্রকৃত-প্রস্তাবে নারীজীবনের অন্ধকার কুলঙ্গিগুলো সবসময়ই যে অন্ধকারাচ্ছন্ন তা নয়, কিন্তু অধিকাংশ নারীর ভেতরেই যে রয়ে যায় অব্যক্ত, অন্তর্গূঢ় কোনো কোনো ক্ষত, সেই কথাটি আরও স্পষ্ট করতেই বিবিধ উদাহরণের অবতারণা। এবং এতে গল্পটি অধিকতর তাজাও হয়ে ধরা দিয়েছে বলা যায়।
৫.
ব্রিটিশবিরোধী বিখ্যাত বিপ্লবী, তুখোড় কমিউনিস্ট কর্মী ও গল্পকার সোমেন চন্দের জীবন থেকে নেওয়া গল্প ‘শোকসন্তাপের দীর্ঘপাঠ’। মাত্র একুশ বছর বয়সে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নৃশংস শিকার সোমেন্দ চন্দ অসামান্য মেধাবী ছিলেন। ডাক্তারিতে ভর্তি হয়েও সমাজতন্ত্র আর মানুষের মুক্তির জন্য পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করা যে মানুষটি ডাক্তারি বই নয়, মার্ক্স-লেলিন-গোর্কিতে মুগ্ধ ছিলেন; তার জীবনটাকে তুলে ধরতে তার মাকেই মাধ্যম করেছেন মনিরা কায়েস। মাত্র চার বছর বয়সে মাতৃহারা হওয়ার পরে ঘরে আসা যে সৎমা, তিনি যে সোমেনকে এতো ভালোবেসেছেন, তার জন্য এমন অসামান্য নিবেদন ছিলো তাঁর, এই গল্পের ভেতরে তা অসামান্য মুন্সিয়ানায় তুলে ধরেছেন গল্পকার।
সোমেন তার মাকে ম্যাক্সিম গোর্কির বিখ্যাত ‘মা’ উপন্যাসের মা করে তুলতে চেয়েছিলেন। মাকে বলেছিলেন, ‘মা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হও। এ বিপ্লব ব্রিটিশ সরকারের ঘেরাটোপে বন্দি নয়। এ আরও বৃহত্তর। তুমি তো ‘মা’ পড়েছো। পারবে না অমন মা হতে?’ ছেলের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান মা সরযু। নারীশিক্ষা মন্দিরে সাতক্লাস পর্যন্ত পড়া সরযু, যার এতদিনকার দৌড় ছিলো নিরূপমা দেবী, অনুরূপা দেবী আর শরৎ চাটুজ্যে পর্যন্ত; তিনি গোর্কির ‘মা’ পড়ে ওর ভেতরে বারুদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছিলেন বটে, তাই বলে ওরকম মা হওয়া ! আরও ছেলেমেয়ে থাকা সত্ত্বেও সোমেনকেই সবচাইতে বেশি ভালোবাসা, সোমেনের জন্য দিনরাত উদ্বিগ্ন থাকা সরযু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলেন ছোট্ট ছেলেটির ক্রমাগত উত্তরণ, বড়ো মানুষের চেয়ে বেশি মানবচিন্তন। মায়ের অনুভব ও বিবরণে সোমেনের গল্প পড়তে পড়তে আমরা পেয়ে যাই অকুতোভয় বিপ্লবী বিনয় বসুকে। পাই কম্যুনিস্ট নেতা রণেশ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু, গোপাল হালদার, কিরণশঙ্কর প্রমুখকেও। মায়ের স্মৃতিমন্থনে হাজির হন সূর্যসেন, প্রীতিলতা, সুভাষচন্দ্র বসু এমনকি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুও। প্রসঙ্গক্রমে নিপীড়িত মানুষের জন্য রচনাসহ উল্লিখিত হন নজরুল ইসলাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মানুষের জন্য কিছু করার উদাহরণ হিসেবে উঠে আসে রবীন্দ্রনাথের নামও। এমনকি প্রগতি লেখক সংঘ ও সোভিয়েত সুহৃত সমিতির প্রদর্শনীর সূত্র ধরে হাজির হন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, জসীমউদ্দীনের মতো লেখক-কবিও। কিন্তু কী-ইবা হলো তাতে ? ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে সহসা সামনে এলো হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গ ও তর্কবিতর্ক। দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি বসবাস করতে থাকা মানুষেরা হঠাৎ উপলব্ধি করলো সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবোধের এক অনাকাঙ্ক্ষিত অসূয় রূপ।
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত সোমেন চন্দের কাহিনি ইতিহাসের সত্য, কিন্তু মনিরা কায়েসের এই গল্পটি ইতিহাসের ঘেরাটোপে বন্দি কোনো কাহিনিমাত্র নয়, এক শোকগ্রস্ত মায়ের আবেগ ও অনুভূতিতে নিহত ছেলের স্মৃতিচারণার রক্তাক্ত শিল্পরূপ। সোমেন চন্দের মায়ের জায়গা থেকে সোমেন চন্দের অবস্থান, অবদান ও আত্মাহুতিকে যে অসামান্য দক্ষতায় শিল্পায়িত করেছেন গল্পকার, তার প্রশংসা না-করে পারা যায় না।
৬.
‘হেঁশেলের হালখাতা’। নামে অনুমান এসে যায়- মেয়েদের হেঁশেল তথা রান্নাঘরের আদ্যপান্ত উপস্থাপন করবেন বুঝি ! একেবারে শুরুতে ডাকরোস্টের অভিনব রেসিপি আর সিদ্দিকা কবিরের ‘রান্না খাদ্য পুষ্টি’ বইয়ের প্রসঙ্গ এই অনুমানের সত্যতা তুলে ধরতে চাইলেও গল্পটি কিন্তু শেষপর্যন্ত আক্ষরিক অর্থে কোনো ‘হেঁশেলের হালখাতা’ হয়ে থাকে না। এটি হয়ে ওঠে দেশবিখ্যাত এক লেখকপত্নীর অন্তর্ক্ষরণের অনিঃশেষ হাহাকার।
গল্পের বিখ্যাত লেখক চরিত্র- শাফকাত। স্ত্রী নাসিমা তাকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন। নাসিমা নিজেও কবিতা লিখতেন, কিন্তু শাফকাতের লেখালিখি, সিনেমা ও নাটক বানানোর জগৎকে সম্পূর্ণ ভারমুক্ত করতে বিয়ের পর নিজের সাহিত্যচর্চার বিষয়টি ভুলে থাকেন। শাফকাত, যার কাছে সাহিত্যে মহৎ বক্তব্য অপেক্ষা মনোরঞ্জনই মুখ্য বিষয়। মনোরঞ্জনের দোহাই দিয়ে মধ্যবিত্তের সেন্টিমেন্টকে পুঁজি করে হালকা সাহিত্যের জোয়ার বইয়ে দেওয়া, দেশের বইয়ের বাজার দখলদারিত্বের চাবি নিজের হাতে নিয়ে নেওয়া এই শাফকাত, যার জন্য প্রকাশকরা অগ্রিম রয়্যালটি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, পঁচিশ শো স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাট বুকিং দেন, তাকে আমরা বাস্তবের বাংলাদেশেই চিহ্নিত করতে পারি। কিন্তু সেদিকে না-গিয়ে আমরা গল্পের ভেতরেই থাকতে চাই।
নিজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে পাকাপোক্তভাবে লেখালিখির কাজে মনোনিবেশ করা এই লেখক-চলচ্চিত্রকারকে তাঁর কাজে যিনি সবচেয়ে বেশি প্রেরণা ও সহযোগিতা দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর সহধর্মিণী। খাবারের প্লেটে বিচিত্র সব আইটেমের যোগান দেওয়া থেকে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম দেখাশোনা, তিনটি মেয়ে লালন-পালন করা এই সহধর্মিণী একসময় উপলব্ধি করেন অকল্পনীয় এক অসহায়ত্ব। নিজের চলচ্চিত্রের নতুন নায়িকার প্রেমে মজে নাসিমাকে দূরে ঠেলতে থাকেন লেখক শাফকাত। লোকমুখে এসব খবর শোনার পরও সুখকর কোনো খবরের অপেক্ষায় নির্লিপ্ত থাকেন নাসিমা। কিন্তু একটি সিনেমার কাজে বরিশালে যাওয়ার পরে সেই ভয়ঙ্কর বার্তাটি পাঠান শাফকাত- আর ফিরবেন না নাসিমার কাছে। নাসিমার পৃথিবীটা ফাঁকা হয়ে যায়। গল্পের শেষদিকে আমরা দেখি শাফকাতের মা এসে মেয়েদের নিয়ে বিখ্যাত লেখকটির জন্মদিন পালনের মধ্য দিয়ে কিছুটা প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাতে কি নাসিমার কোনো কল্যাণ নিহিত আছে? না। জন্মদিনের আয়োজনে শাফকাতের প্রিয় খাবার-দাবার রান্না করে দিলেও নাসিমা জানে তার নিজের হৃদয়ে কোনো রান্না নেই। ‘আজ অরন্ধন।’
আবারও বলি, এই গল্পটির উদ্দিষ্ট চরিত্রটি বাস্তবের বাংলাদেশ থেকেই নেওয়া। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটি শেষপর্যন্ত সাহিত্য। স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির একজন কথাশিল্পীর হাতে তৈরি গল্প, যেখানে একজন লেখক বা বিখ্যাত কোনো ব্যক্তির খ্যাতিমান হওয়ার পিছনের ব্যক্তিটির পরাজিত হৃদয়ের অন্তর্দহন লুক্কায়িত। তাইতো প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়েন তলস্তয়-সোফিয়া, অমর্ত্য সেন-নবনীতা, কমলকুমার-দয়াময়ী দম্পতিদের কথাও। যে নাসিমা একদিন বুদ্ধদেব বসু-প্রতিভা বসু, নরেন্দ্র দেব-রাধারানী দেবী, আবু সয়ীদ আইয়ুব-গৌরী আইয়ুবের জায়গায় ভাবতেন নিজেদেরকে, সেই নাসিমা নিজের এমন পরিণতিকে পরাজিত ও প্রতারিত নারীত্বের প্রতীক হিসেবে ভাববেন, সেটাই স্বাভাবিক।
আর হ্যাঁ, মনিরা কায়েসের অন্যান্য গল্পের মতোই এখানেও আমরা গল্পের ভেতরে পেয়ে যাই অনেক গল্প-অণুগল্পকে, যা লেখকের বুনন কৌশলের স্বতন্ত্রতাকে আমাদের সামনে আবারও উচ্চকিত করে তোলে। আর গল্পকারের ধৈর্যশক্তিকেও করে পরীক্ষিত।
৭.
নগর সভ্যতার আগ্রাসনে রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের ভিটেমাটি হারিয়ে উধাও হওয়া; পরাশক্তি রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে ন্যায়বাদী রাষ্ট্র ও সমাজের বিনির্মাণ বিপর্যস্ত হওয়া কিংবা মুক্তবাজার অর্থনীতি ও মুনাফালোভী মানুষের আগ্রাসনে প্রকৃতি ও পরিবেশের স্বাভাবিকত্ব বিনষ্ট হওয়ার কাহিনিগুলো আমাদের জানা। এসব জানা কাহিনিগুলোকে আত্মলব্ধ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে জারিত করে মনিরা কায়েস লিখেছেন ‘যেভাবে রাষ্ট্র ধনী হয়ে উঠতে পারে’ গল্পটি।
অন্য গল্পগুলোর মতো এই গল্পটিতেও কেবল কাহিনিতে নয়, চরিত্রের নামেও আমরা চেনা মানুষের গন্ধ পাই। শিল্প-সাহিত্য জগতের মানুষের পানাসক্তি, সেই সূত্রে শাহবাগের ওয়াসি-শহীদুল্লাহদেরকে পেরিয়ে বিটলসের এলভিস প্রিসলি কিংবা কবি অ্যালেন গিন্সবার্গের কথা যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে আমাদের সমাজের নানান সংস্কার-কুসংস্কারের কথাও। গল্পের কেন্দ্রে থাকা ওয়াসী তার সন্তান প্রসবোন্মুখ স্ত্রী নাজকে নিয়ে যখন নার্সিং হোমের দিকে যাত্রা করে, তখন প্রসবক্রিয়া যাতে নিষ্কণ্টক হয়, সেজন্যে নাজের শাশুড়ি শুকনো মরিয়ম ফুল ভিজিয়ে রাখে পানিতে। এমনকি সন্তান প্রসবের পরে নার্সদের চোখ এড়িয়ে ঢেমশি ফুলের একফোঁটা মধুও ঢেলে দেয় সদ্যজাত কন্যার মুখে। নাম নিয়েও সংস্কার-সংস্কারহীনতায় হয় টানাটানি। কিন্তু এসব ব্যক্তিগত বিষয়গুলো গল্পের মূল আলেখ্য নয়, মূল আলেখ্য হিসেবে ধরা দেয়- বাঙালি সেটেলারদের ঘায়ে আদিবাসীদের ‘মহুলপুর’ গ্রামের নাম ‘কাবুলিপাড়া’ হয়ে যাওয়া, নগরায়ণের আগ্রাসনে অরণ্য-পাহাড়ের মহিমা হারিয়ে যাওয়ার মতো নৈর্ব্যক্তিক বিষয়গুলো। ওয়াসীর স্মৃতি ও দর্শনে আমরাও উপলব্ধি করি সভ্যতা ও রাষ্ট্রের আগ্রাসনের ইতিবৃত্তের অংশবিশেষ।
ষাট-সত্তর-আশির দশকজুড়ে মার্কিন আগ্রাসনের কবলে কী ধরনের মাৎস্যন্যায় সংগঠিত হয়েছে দেশে দেশে, উনিশ শো চুয়াত্তর সালে মার্কিনিদেরই চক্রান্তের রোষাণলে বাংলাদেশে কীভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, সেসব কথাও অব্যক্ত রাখেন না গল্পকার। এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের মিত্রদের কাছে সবচেয়ে বড়ো শত্রু যে কিউবা এবং তাদের মিত্র দেশগুলো, প্রসঙ্গক্রমে সেকথাও জানিয়ে দেন তিনি। ইলা মিত্রের মতো প্রতিবাদী মানুষের অবর্তমানে সাঁওতালদের মতো আদিবাসীরা উধাও হয়ে যাচ্ছে, প্রকৃতির প্রকৃত রূপ পরিবর্তিত হয়ে সুযোগসন্ধানী মুনাফালোভীদের করতল বিস্তৃত হচ্ছে দিনে দিনে।
গল্পের শেষদিকে আমরা দেখি, এই আগ্রাসনের কবলে পড়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী মানুষের স্মৃতিস্তম্ভের নিশানা দানকারী সেই বিরাট বটগাছটিরও কোনো চিহ্ন নেই কোথাও। অশ্রুসিক্ত হয়ে মুষড়ে পড়ছে ওয়াসী। তখন তার কাছে সান্ত্বনা হিসেবে হাজির হচ্ছে বাইবেলের সেই বাণী ‘যিনি জীবিত আছেন তাঁকে তোমরা মৃতদের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন?’
ইতিহাস-ঐতিহ্য-প্রকৃতি বিকৃতিকারী নগরসভ্যতা ও রাষ্ট্রের আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিতৃষ্ণ মনোভাবে গল্পটির সমাপ্তি ঘটে।
৮.
সাহিত্য জীবন নিয়ে এক ধরনের নান্দনিক ভাষ্যরচনা। সাহিত্যিকমাত্রই জীবনের ভাষ্যকার। এটাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য পূরণে তিনি কতোটা সফল হবেন, তা নির্ভর করে বেশকিছু উপাচারের উপর। বিষয় অবশ্যই সেগুলোর মধ্যে প্রথম, কিন্তু শিল্পের নিরিখে সেটি প্রধানতম আকর্ষণ নয়। প্রধানতম আকর্ষণ; বোধকরি বলবার ধরন, অর্থাৎ বিষয়টাকে সাহিত্যিক কীভাবে উপস্থাপন করছেন?
মনিরা কায়েস তাঁর এক-একটি ছোটগল্পের ভেতরেই ঢুকিয়ে দেন অনেক গল্প-অণুগল্প এবং প্রাসঙ্গিক বিবিধ অনুষঙ্গমালা। কেউ একে বলতে পারেন- গল্পের ভেতরেই উপন্যাসের প্রণোদনা, কিন্তু আমার কাছে মনে এটাই জীবনসত্যের প্রকৃত ব্যঞ্জনা। আমরা যখন কোনো একটি কাজ করি, সেটা শারীরিক কিংবা মানসিক যা-ই হোক, আসলে কি একটিমাত্র কাজ করি? না। একইসঙ্গে আমরা অনেক কাজ করি, অনেককিছু ভাবি। শারীরিকভাবে সেটা সবসময় দৃশ্যযোগ্য না-হলেও মানসিকভাবে যে আমরা প্রতিনিয়তই বহুবিধ ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকি, আমাদের মন একইসঙ্গে যুক্ত ও বিযুক্ত হন নানারকমের ক্রিয়ার সঙ্গে, স্মৃতি-কল্পনা-ভবিষ্যতের সমুদ্রে ভেসে বেড়ান, একটু ভেতরে ডুব দিলেই সেটা আমরা জেনে যাই। এই জানাটাকে ভাষায় চিত্রায়িত করার দায়িত্ব নিতে গিয়ে মনিরা কায়েস যে একই গল্পের ভেতরে অনেক গল্প জুড়ে জুড়ে তাঁর ভাষ্য রচনা করেন, সেটাকে আমরা যদি জীবন সত্যের যথার্থ ব্যঞ্জনা বলি, অধিকতর উপযুক্ত মনে হয়। ‘অন্ধ কুলঙ্গির টীকাভাষ্য’-তে এই ব্যঞ্জনাই তিনি রচনা করেছেন তিনি। হাটের কোলাহল উজিয়ে নিজস্ব মৃত্তিকায় বুঁদ থেকে তুলে ধরেছেন অন্তর্গূঢ় জীবনের অন্তর্ভেদী প্রতিচ্ছবি।
ঢাকা/তারা
আরো পড়ুন