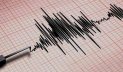গুপ্তচরের চোখ ফাঁকি দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে দেশত্যাগ
সঞ্জয় দে || রাইজিংবিডি.কম

সারায়েভো টু বার্লিন: চতুর্থ পর্ব
প্রথম ব্যারিকেড পার হলেও যাতে মূল দেয়ালে পৌঁছুবার আগেই পলায়নকারীকে গুলি করে মারা যায়, সেজন্যেই ছিল এতোসব আয়োজন। তবে মুক্তির সন্ধান পেতে মরিয়া যারা, তাদের কি সত্যিই ঠেকানো যায়? তারা তো কোনো-না-কোনো পন্থা বার করবেই। হলোও তাই।
অনেকেই শ্রমসাধ্য সুড়ঙ্গ খোঁড়া শুরু করলেন। পূর্বের দিক থেকে সুড়ঙ্গ খোঁড়া সহজ ছিল না। এ ক্ষেত্রে মূলত পশ্চিমে থাকা আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব চাঁদা তুলে, পরিকল্পনা করে তাদের দিক থেকে সুড়ঙ্গ খোঁড়া শুরু করে দিতেন। সীমানার খুব কাছের কোনো পরিত্যাক্ত বাড়ি বা গুদাম ঘর থেকে শুরু হতো এই সুড়ঙ্গের কাজ। প্রচণ্ড ঝুঁকিপূর্ণ ছিল সেই কাজ। সুড়ঙ্গের ভেতর দুর্ঘটনার আশঙ্কা তো ছিলই, সেইসঙ্গে ছিল গোয়েন্দাদের নজরে পড়ে যাবার ভয়। গোয়েন্দা মানে পশ্চিমের নয়, পূর্বের। কারণ, পশ্চিম বার্লিনেও তখন পূর্ব বার্লিনের বহু গুপ্তচর ঘুরঘুর করতো।
গুপ্তচরের প্রসঙ্গে দুটো কথা হয়তো না বললেই নয়। জাঁদরেল গুপ্তচর সংস্থা বলতে আমরা জানি কেজিবি কিংবা সিআইএ-এর নাম, কিন্তু তৎকালীন পূর্ব জার্মানির স্তাজিকেও অনায়াসে কুখ্যাত গুপ্তচর সংস্থার কাতারে ফেলা যায়। ছোট্ট এই দেশটির প্রতি তিনজনের একজন কোনো-না-কোনোভাবে এই সংস্থার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। কেও ইচ্ছায়, কেওবা হয়তো চাপের কাছে নতি স্বীকার করে। আর সেভাবেই রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের শোবার ঘর অবধি বিস্তৃত হয় সংস্থাটির সুদীর্ঘ কালো হাত। বার্লিন দেয়াল ভেঙে ফেলার পর তেমন গোপন ব্যক্তিগত তথ্য সম্বলিত লক্ষ লক্ষ ফাইলের সন্ধান পাওয়া যায় এর সদর দপ্তরে। কেজিবি নিজের হাতে তৈরি সংস্থাটি শুধু আভ্যন্তরীণ তথ্যই নয়, তৎপর ছিল ইঙ্গ-মার্কিন বলয়ের গোপনীয় তথ্য সংগ্রহেও।

একইসঙ্গে তাদের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম জার্মানিতে নানা অঘটন ঘটানো, আর নিজ দেশের মানুষের পশ্চিমে পলায়ন ঠেকানো। দুই জার্মানি একত্র হবার পর ফ্রাঙ্কফুর্ট আর আলে সড়কের পাশেই অবস্থিত এর প্রকাণ্ড সদর দপ্তরটিকে ধ্বংস বা ভিন্ন কিছুতে বদলে না ফেলে রূপান্তর করা হয় জাদুঘরে। নিরাপরাধ মানুষকে গুম বা জিজ্ঞাসাবাদের কল্পে ব্যবহৃত বারকাস বি-১০০০ মাইক্রোবাস থেকে শুরু করে স্তাজির অফিস, সভাস্থল, ইত্যাদি রাখা হয়েছে অবিকল, অবিকৃতভাবে; যাতে পরবর্তী প্রজন্ম সেই তমসাচ্ছন্ন সময়কে স্মৃতির অতলে হারিয়ে না ফেলে। ভাগ্যিস সেটা করা হয়েছিল! নয়তো গত বছর বার্লিনে এসে ইতিহাসের সেই কালো অধ্যায়ের সন্ধান পেতাম কী করে!
বলছিলাম বার্লিন দেয়ালের নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কথা। স্তাজির শ্যেনদৃষ্টি আর আনুষঙ্গিক সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করে খুব স্বল্পসংখ্যক মানুষই শেষ পর্যন্ত পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছিলেন। বহুকাল আগে আমার দেখা ‘বার্লিন টানেল ২১’ সিনেমাটি ছিল তেমনই এক ঘটনাকে উপজীব্য করে নির্মিত। আশির দশকে সত্য কাহিনী অবলম্বনে তৈরি সেই সিনেমাটিতে দেখানো হয় তেমনই একদল অদম্য সাহসী যুবকের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সুড়ঙ্গ খুড়বার গল্প, যে সুড়ঙ্গ শেষ পর্যন্ত ওপার থেকে নিয়ে আসে তাদের প্রিয়জনদের।
‘বার্লিন টানেল ২১’ সিনেমার নামের শেষে যুক্ত থাকা নম্বরটিকে আমি শুরুতে ভেবেছিলাম কেবলই একটি শনাক্তকারী সংখ্যা। কিন্তু স্বচক্ষে ‘টানেল ৫৭’ দেখতে গিয়ে জানলাম এক ভিন্ন কথা। এই সংখ্যাটি দিয়ে মূলত বোঝান হতো ঠিক কতজন মানুষ প্রাণ নিয়ে এই টানেলের মাঝ দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে গেছেন, সেটি।
‘টানেল ৫৭’-এর তত্ত্বাবধান করে একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা। এটি যে মাঠের মাঝ দিয়ে গড়া হয়েছিল, তার দুই ধারে আজ ব্যস্ত বসতবাড়ি। টানেলের জায়গায় মাটি যাতে ধ্বসে না পড়ে, সে জন্যে ঘাসের মাঝে-মাঝে স্টিলের পাত বসানো কিছু দূর পরপর। আমরা সেই টানেলের প্রবেশ মুখে ঢোকার জন্যে বারনাওয়ার নামক পাতাল রেলস্টেশনে ঢুকলাম। হুসহাস করে পাশ দিয়ে তীব্র গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে ট্রেন। স্টেশনের ভেতর দিয়ে টানেল খোঁড়ার পেছনে কারণ আছে। এই স্টেশনটির অবস্থান ছিল পূর্ব বার্লিনে। অন্যদিকে এটি ব্যাবহার করে যে ট্রেনগুলো পার হয়ে যেত, সেগুলো ছিল পশ্চিম বার্লিন বা পশ্চিম জার্মানির।

অর্থাৎ এক দেশের ভেতর দিয়ে আরেক দেশের ট্রেন চলে যাওয়া। যে দেশটি কিনা আবার চরম শত্রু দেশ। ফলে এই স্টেশনে কেউ নামতে বা উঠতে পারতো না। প্রবেশমুখ ছিল তালাবদ্ধ। লোকে বলত– ভুতুড়ে স্টেশন। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই হয়তো কেউ এর পাশ দিয়ে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার ফন্দি এঁটেছিল। তো আমরা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের পার্শ্বস্থিত এক গুপ্ত দরজার মাঝ দিয়ে গেলাম সুড়ঙ্গের সঙ্কীর্ণ স্থলে। দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে যারা টানেলটি খুঁড়ছিলেন, তাদের ব্যবহৃত মাটি সরাবার ট্রলি এখনো একইভাবে অবিকৃত আছে। পড়ে আছে কাঁদামাখা টর্চ, দস্তানা, হেলমেট। যেন খুঁড়তে খুঁড়তে ক্লান্ত হয়ে তাঁরা আশেপাশেই কোথাও গেছেন সিগারেট ধরাতে; ফিরে এসে আবার হয়তো হাত লাগাবেন ওপারে যাবার পাতালপথ তৈরির কাজে।
সেবারে এই টানেল দর্শন শেষে ওপার থেকে আসা শরণার্থীদের স্মৃতিবিজড়িত আরেকটি ক্যাম্পে গিয়েছি, যেটি ছিল শরণার্থীদের প্রাথমিক ঠিকুজি। ক্যাম্পটি পূর্ব বার্লিনের মারিয়েনফেলড-এ। ৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই শিবিরে দরজা মাড়িয়ে নব্বই অবধি পূর্ব থেকে পশ্চিমে এসেছিলেন প্রায় তের লক্ষ শরণার্থী। ওখানে এসেই সবাই প্রথমে নাম লেখাতেন, পশ্চিমে বাস করার বৈধ কাগজপত্র পাবার জন্যে। যাঁদের কোথাও যাবার জায়গা নেই, সেখানেই কিছুদিনের জন্যে থাকার বন্দোবস্ত হতো। শিবিরের প্রতি রুমে লৌহ নির্মিত দোতলা বাঙ্কবেডে মোট চারজনের থাকবার ব্যবস্থা। উঁচু সিলিং। দুদিকের খাটের মাঝে ছোট্ট একটি টেবিল। পড়া কিংবা খাবার জন্যে। কোণের দিকে ছোট্ট আলমারি। ঘরের একধারে তিনপাল্লার কাচের জানালা। ও-পাশটায় বাগান। সেইসঙ্গে আছে কমন কিচেন। ক্যাম্পের শোকেসে রাখা রুলটানা খাতায় সেই পঞ্চাশের দশক থেকে আগত প্রতিটি শরণার্থীর নাম কালির কলমে লেখা আছে। কোনো তথ্যই হারিয়ে যায়নি। জার্মানদের এই তথ্য সংরক্ষণের সংস্কৃতিকে কুর্নিশ করতেই হয়।
সেই শিবিরটি কিন্তু এখনো পরিত্যাক্ত নয়। এককালে যেটি ব্যবহৃত হতো ওপারের জার্মানদের স্বাগত জানাতে, আজ সেটি স্বাগত জানায় সিরিয়া, ইরাক কিংবা আফগানিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের। ক্যাম্পের পেছনের চত্বরে বেশ কিছু আরব শিশু খেলছে। বারান্দায় বসে ওদের দিকে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে জনা দুয়েক মহিলা। ওদের মা হয়তো। এইসব শরণার্থী শিশুদের নানা ছবি আর গল্পকথাও ঝুলছিল ক্যাম্পের একদিকের দেয়ালে। একটি ছবির গল্প ছিল এমন– ‘আমার নাম ইসমাইল। বয়স ১২ বছর। সিরিয়া থেকে পালিয়ে বাবা-মায়ের সাথে বার্লিনে আসি ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। আমি এখন একটু একটু করে জার্মান শিখছি। এই ক্যাম্পেরই একটি স্কুলে ভর্তি হয়েছি। স্কুলে বেশ কয়েকজন নতুন বন্ধু পেয়েছি। বার্লিন আমার খুব ভালো লাগে।’

সেদিন মারিয়েনফেলড থেকে ফেরার পথে রেল স্টেশনে পরের ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। দেখি পাশেই নোটিশ বোর্ডে এক রঙিন পোস্টার সাঁটা। কার্টুনের মাধ্যমে একজনের কাঁধে ঝুলিয়ে রাখা ব্যাগের ছবি এঁকে বলা হয়েছে, ব্যাগ সামলে রাখুন। নইলে কোন ফাঁকে চোর সব সাফা করে দেবে, টেরও পাবেন না। এমন পোস্টার আর সাবধানবাণী এর আগেও চোখে পড়েছে। শোয়েনফিল্ড এয়ারপোর্টের আগমন লাউঞ্জে পা ফেলতেই শুনি, মাইকে বারবার বলা হচ্ছে, পকেট সামলে রাখুন। এমন পিলে চমকানো বাণী শুনে তো নিজের অজান্তেই হাত চলে যায় পেছনের পকেটে, টাকার থলে ঠিক আছে কিনা, দেখে নিতে। অথচ নব্বই-এর দশক অবধিও কিন্তু জার্মানি থেকে ফিরে গিয়ে সবাই বলত, এ এমন এক দেশ, যেখানে রাতে দরজা খুলে শুলেও চোর-ছ্যাঁচড়ের ভয় নেই। বোঝা যায়, সেই দিন বিগত। মূলত নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে দারিদ্র্য ভয়াবহ রূপ ধারণ করলে সেখান থেকে আসা অনেকেই এমন নানা অপকর্মের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। কারণ, এ ধরনের কাজগুলোতে শ্রম কম, মুনাফা বেশি।
আমি নিজেই একবার এদের পাল্লায় পড়ে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। সেবারে বার্লিন ওয়ালের যে অংশটুকু এখনো অক্ষত, তার আশেপাশে হেঁটে বেড়িয়ে ছবি তুলছি। হঠাৎ দেখি, একটি ছেলে, বয়স হয়তো বছর পনের-ষোল হবে, আমার কাছে একটি কাগজ এনে সই চাইছে। কী এক মূক ও বধির সংগঠনের পক্ষে কোনো আবেদনের স্বপক্ষে। চেহারার দেখেই বোঝা যায়, ছেলেটি জার্মান নয়, রোমানিয়ান-বুলগেরিয়ান জিপসি হবে। আমি তাকে অগ্রাহ্য করে সামনে এগিয়ে গেলাম। ছেলেটিও আমাকে আর না ঘাঁটিয়ে পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া দুই জাপানি তরুণীর দিকে ছুট লাগালো। পরে ওই স্থানের কয়েক গজ দূরেই দেখি, বিজ্ঞপ্তি টানিয়ে লেখা– মূক-বধির সংগঠনের পক্ষে কোনো স্বাক্ষর চাইতে এলে দেবেন না, এরা ঠগ। আপনার মূল্যবান জিনিশ হাতিয়ে আলগোছে চম্পট দেবে। সেটা দেখে না হেসে পারিনি। এখানেই এই বিজ্ঞপ্তি টানানো, আর একে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অল্প দূরেই সেই ছোকরা পরবর্তী শিকারের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। (চলবে)
পড়ুন তৃতীয় পর্ব: হোটেলে রুমের জন্য বার্লিনে উদ্ভট শর্ত
ঢাকা/তারা
আরো পড়ুন