আমার বন্ধু গিয়াসউদ্দীন
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী || রাইজিংবিডি.কম
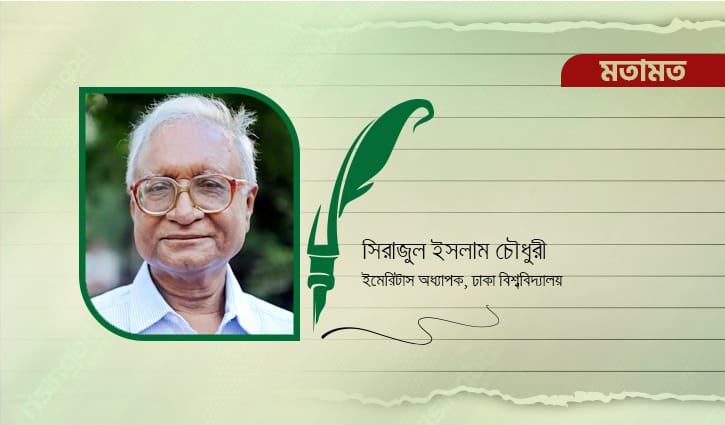
একাত্তরের গণহত্যায় ত্রিশ লক্ষ শহীদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরাও ছিলেন। যাঁদের পরিকল্পিতভাবে বাছাই করে হত্যা করেছিল আল-বদর বাহিনী। তাঁদের অনেকেই আমার শিক্ষক, সহকর্মী, বন্ধু অত্যন্ত আপনজন। আমি আমার বন্ধু শহীদ বুদ্ধিজীবী গিয়াসউদ্দীনকে নিয়ে এখানে বলছি।
গিয়াসউদ্দীন আহমদের সঙ্গে আমি স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়েছি, চাকরিও করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখন আমি আছি, সে নেই। গিয়াসউদ্দীন বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাড়েনি, আমার অবস্থাও তথৈবচ। বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি ভালোবাসতাম, সে বোধ করি ভালোবাসত আমার চেয়েও বেশি। নইলে একাত্তরে আমরা অনেকেই যখন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছেড়ে প্রায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলাম, তখন গিয়াসউদ্দীন রয়ে গেল কেন? এই ভয়ঙ্কর সময়টাতে ক্লাসটাস যা হতো সে তো প্রহসন মাত্র, গিয়াসউদ্দীন ছিল মহসিন হলের হাউস টিউটর। সেখানে তখন থাকত অসহায় কয়েকজন ছাত্র, যাদের ওপর হানাদাররা একাধিকবার চড়াও হয়েছে, আর ছিল আমাদের গিয়াসউদ্দীন, তাঁর ছিল ভালোবাসা, আর ছিল দায়িত্বজ্ঞান।
১৪ ডিসেম্বর হানাদারদের পরাজয় ঘনিয়ে এসেছে, সেই সময়ে বিপন্ন ছাত্ররা খাবার পানি পাচ্ছে না দেখে, সরবরাহ ব্যবস্থায় ত্রুটি দূর করা যায় কিনা সেটা দেখতে বের হয়েছিল গিয়াসউদ্দীন, সে অবস্থাতেই আল-বদরেরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। আর ফেরেনি।
তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা যুদ্ধের সময়েই। আগস্ট মাসে বোধ করি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রয়াত শিক্ষক জয়নুল আবেদীন আর আমি গেছি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সন্ধ্যার পরে। গিয়াসের ছোট ভাই চিকিৎসক রশীদউদ্দীন আহমদ চলে যাবে দেশের বাইরে। গিয়াস তাঁকে সাহায্য করছে। গিয়াসউদ্দীন যাবে না, দেশের ভেতরেই তাঁর অনেক কাজ। তা ছিল বৈকি। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করছিল সে, সীমান্ত পার হতে। আমরা দু’জনেও আলাপ করলাম। গিয়াস বললো, পথঘাটের খবর সে জানে, অসুবিধা হবে না যেতে চাইলে। জয়নুল আবেদীন চলে গিয়েছিলেন এর কিছুদিন পরেই। আমার আর যাওয়া হয়নি।
পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর চোখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও শিক্ষকদের ক্লাব দু’টিই ছিল মারাত্মক প্রতিষ্ঠান। সেখানে শিক্ষকরা নিয়মিত রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা চালাত বলে তারা নিশ্চিত ছিল এবং ছাত্ররা যে বিপথগামী হয়েছে তার জন্যও তারা শিক্ষকদেরকেই সরাসরি দায়ী মনে করতো। সে জন্য ২৫ মার্চ রাত্রে তারা ছাত্রাবাস তো বটেই শিক্ষকদের আবাস এবং তাদের ক্লাবের ওপরও ট্যাঙ্ক ও কামান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ক্লাবে তখন কোনো শিক্ষক ছিলেন না, থাকবার কথা নয়, কিন্তু এতোই উন্মত্ত ছিল ওই হানাদাররা যে তারা পার্থক্য করেনি। নিরীহ কর্মচারী যারা ওই ভবনে ঘুমাচ্ছিল তাদের কয়েকজনকে হত্যা করেছে। ছাত্রাবাসে ছাত্রহত্যা ও শিক্ষকদের ঘরে ঢুকে শিক্ষক হত্যার ব্যাপারে সে-রাতে তাদের কোনোরকম দ্বিধা বা বাছবিচার দেখা যায়নি। গিয়াসউদ্দীন এসব ঘটনা অনুপুঙ্খ জানত; কিন্তু সে ক্যাম্পাস ছাড়েনি। কর্তব্যবোধের শৃঙ্খলে আটকা পড়ে গিয়েছিল।
সেই ১৯৪৮-এ দেখা; না দেখে তো কোনো উপায়ই ছিল না। গিয়াস তো দশজনের ভেতর একজন ছিল না, সে ছিল একজনের ভেতরই দশজন। ক্লাস রুম, বয়স্কাউটের দল, বাস্কেট বলের মাঠ, কোথায় সে ছিল না। সর্বত্রই নেতা সে। তাছাড়া আমি তখন এসেছি বাইরে থেকে, কাউকে চিনি না, শিক্ষকদের তো বটেই, ছাত্রদেরও কৃপাপ্রার্থী; আর গিয়াস হচ্ছে সবচেয়ে পুরাতন ছাত্রদের একজন; থাকে সে স্কুলের কাছেই, পড়ছে সেই ক্লাস ওয়ান থেকে। স্বাস্থ্যশ্রী’তেও চমৎকার!
আর ওই যে গলার স্বর সেটা যাবে কোথায়? তাঁকে সে লুকায় কোন উপায়ে? আমাদেরই সহপাঠীদের একজন, যাদের সোনার ব্যবসা ছিল, রায় স্যার বলতেন বুলিয়ন ‘মার্চেন্ট’, তারা নতুন সিনেমা হল খুলেছিল তাঁতিবাজারের মোড়ে, নাম দিয়েছিল ‘নাগরমহল’, সেই বলত, তাদের সিনেমা হলে নতুন শব্দযন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে যেমনটি আর কোনো প্রেক্ষাগৃহে নেই, নাম তার আরসিএ সাউন্ড সিস্টেম। ব্যস আর যায় কোথায়? ওই নামই চালু হয়ে গেল গিয়াসের- আরসিএ সাউন্ড সিস্টেম।
গিয়াস জানত সেটা। উচ্চৈঃস্বরে হেসে বলতো, কই, আমি তো আস্তে আস্তেই কথা বলি। এখন মনে হয় জোরটা যে কেবল গলারই ছিল তা নয়, ছিল তাঁর মনেরও। সে ক্ষমতা রাখত ধমক দেবার, ধমকে দেবার। অথচ অতিশয় কোমলও ছিল আমাদের এই বন্ধু। সাহায্য করতে এগিয়ে আসত। খোঁজখবর নিত।
ক্লাস নাইনে আমাদের পাঠ্য ছিল চার্লস রিডের লেখা একটি উপন্যাস। ‘দি ক্লয়েস্টার অ্যান্ড দি হার্থ’। চরিত্রগুলোর মধ্যে একজনের নাম ছিল গাইসব্রেকট। আমরা নিজেদের মধ্যে গিয়াসকেও ওই নামে ডাকতাম। কোনো দিক দিয়েই উপেক্ষণীয় ছিল না সে। ইংরেজি পড়াতেন আমেরিকান পাদ্রি, ব্রাদার লরেঞ্জো। মাঝেমধ্যে তিনি আমাদের ইংরেজি শব্দের বাংলা জিজ্ঞাসা করতেন। শব্দার্থ হিসেবে একবার আমরা বলেছি ‘দরজা’, গিয়াস দাঁড়িয়ে বললো, ‘না, দরওয়াজা’। আলাদা ছিল সে, অন্যদের থেকে।
আমরা যে বছর ম্যাট্রিক দিই ঠিক তার আগের বছরই স্কুলে কলেজ খোলা হয়েছে। ছাত্রভর্তির ব্যাপারে প্রিন্সিপাল ফাদার হ্যারিংটন ছিলেন বেশ তৎপর। অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। গিয়াসউদ্দীনের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল যে সে ওই কলেজে ভর্তি হবে। ওদের বাসা খুব কাছেই, তাছাড়া সে হচ্ছে স্কুলের আদি ছাত্রদের একজন। তবে আমি থাকতাম বেশ দূরে। বেগম বাজারে। কিন্তু ফাদার হ্যারিংটন বোধ করি আমার আব্বাকে বুঝিয়ে ফেলেছিলেন যে তাদের নতুন কলেজে ছাত্রদের যত্ন নেওয়া হবে বিশেষভাবে; আর আমার আব্বা কিছুটা শঙ্কায় ছিলেন বড় কলেজে গিয়ে না-জানি কোন বিপদে পড়ে তাঁর সাদাসিধে ছেলেটা; তাই আমি যখন অন্য বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছি ঢাকা কলেজে তখন আমার পিতা এক বিকেলে আমার হাতে কয়েকটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, নতুন কলেজে ভর্তির কাজ তিনি সম্পন্ন করে দিয়েছেন; আমাকে আর ছোটাছুটি করতে হবে না।
কলেজে গিয়ে দেখি গিয়াস আছে। এলো রশীদুজ্জামান, কলকাতায় যে আমার সহপাঠী ছিল। মাদারীপুর থেকে এসেছে শাহ জামান, থাকছে কলেজ হোস্টেলে। আর মানিকগঞ্জের ইব্রাহিম।
ছাত্র খুবই অল্প। তবে অল্পদিনেই কলেজ বেশ জমে উঠল। মনে রাখবার মতো ঘটনা ছিল। শেক্সপীয়ারের ‘টেমপেস্ট’ নাটকের মঞ্চায়ন। মূল ইংরেজিতে এবং কোনো অংশ বাদ না দিয়ে। অদম্য উৎসাহ ছিল ভাইস-প্রিন্সিপাল ফাদার মার্টিনের। তাঁর বয়স অল্প, ত্রিশের কমই হয়তো; থাকতেন কলেজের চিলেকোঠায়, সেখানে গেলে তাঁর চুরুটের মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যেত।
নাটকে অভিনয় প্রায় বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছিল। সে বছর খুলনাতে ঝড় হয়েছে, পীড়িতদের সাহায্যার্থে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। আমরা রিহার্সেল দিতাম, আবার টিকিট বিক্রি করার কাজেও অংশ নিতাম। ফাদার মার্টিনের উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল।
নাটকটি খুব জমেছিল। স্কুলের বারান্দাকে মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে স্কুলের মাঠে তাঁবু টানিয়ে চেয়ার বিছিয়ে দর্শকদের জন্য বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথমে কথা ছিল এক রাত্রের, পরে সাফল্য দেখে পরপর দু’রাত মঞ্চায়ন ঘটেছে।
সে নাটকে গিয়াসের ভূমিকাটি তাঁর স্বভাবের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। সে সেজেছিল গঞ্জালো। স্বপ্নদ্রষ্টা, প্রায়-সন্ন্যাসী। সাদা দাড়ি, পাকা চুল, মস্ত জোব্বা পরে সে ঢুকত সাধুর মতো, আর ওই যে তাঁর বিখ্যাত গলা, সেই গলাতে বলতো এক স্বপ্নের পৃথিবীর কথা।
আমি সেজেছিলাম ক্যালিবান। ওই নাটকে ক্যালিবানই যে সবচেয়ে ‘মুক্ত’ চরিত্র সেটা অভিনয় করতে গিয়ে সেদিন টের পেয়েছি। প্রসপেরোই কর্তা, কিন্তু সে সর্বদাই সন্ত্রস্ত তার কিশোরী কন্যাটির নিরাপত্তা নিয়ে। এ্যারিয়েল বায়বীয়, কিন্তু সে আজ্ঞাবহ ভৃত্য, প্রসপেরোর। ক্যালিবানের ভয়-ডর নেই, নেই দাসের হীনম্মন্যতা। দ্বীপের সে মালিক, বর্তমানে অধিকারচ্যুত, তাই সে বিদ্রোহী। প্রবলভাবে বিদ্রোহ করে, আর যন্ত্রণায় কাতরায়, কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করে না। ‘টেমপেস্ট’ নাটকের সবচেয়ে সুন্দর কাব্যিক সংলাপগুলোর বেশ কিছু অংশ যে নাট্যকার ক্যালিবানকে দিয়ে দিয়েছেন সেটা বুঝেছি অভিনয় করতে গিয়ে। ক্যালিবান একাধারে ভয়ঙ্কর ও কৌতুককর। যে জন্য তাকে উপস্থিত হতে দেখলেই দর্শক নড়েচড়ে বসতো। কখনো নীরবে শুনতো, কখনোবা হাস্য করতো সবেগে।
এই বর্ণনাটির একটি প্রাসঙ্গিকতা আছে। গঞ্জালোর সংলাপেও উৎকৃষ্ট কবিতা ছিল, গিয়াস তা আবৃত্তিও করতো আবেগ দিয়ে। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল দর্শক তেমন সাড়া দিচ্ছে না। দ্বিতীয় রাতে বিরতির সময়ে কথাটি সে বলেই ফেলল, ‘ধ্যাৎ, সিরিয়াস কথা লোকে শুনতে চায় না। তোমাদের তিনজনের (ক্যালিবান ও তার দুই সঙ্গী ট্রিস্কুলো ও স্টেফনোর) কথা শুনে, ভাবভঙ্গি দেখে হেসে কুটিকুটি হয়।’
অথচ গিয়াসের পক্ষে তো কখনো কোনো অবস্থাতেই সিরিয়াস না-হয়ে উপায় ছিল না। সেটি তো ছিল তাঁর স্বভাবজাত। হাস্যকৌতুকে যে তাঁর কিছু কম উৎসাহ ছিল তা নয়, কিন্তু যখন হাসত তখনো মনে হতো সে গম্ভীর, আমাদের মতো বাচাল নয়।
অন্যদের কেমন মনে হতো জানি না, কিন্তু আমার কাছে অনেক সময়ে ঠেকত যেন সে একজন মুরব্বি। অল্পবয়সীদের জন্য তো বটেই, আমরা যারা তাঁর সমবয়সী ছিলাম তাঁদের জন্যও। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভর্তি হয়েছি, কিন্তু সাবসিডিয়ার ছিল একই, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি। একদিন দুপুরে কমনরুমে খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে খেয়াল ছিল না, যখন দেখলাম দেরি হয়ে গেছে, তখন আর ক্লাসে যাইনি। পুরাতন সেই কলা ভবনের সিঁড়ির কাছে গিয়াসের সঙ্গে দেখা, বললো, ‘কি, ক্লাসে যে দেখলাম না?’ বললাম, ফস্কে গেছে। গিয়াস বলল, ‘দেখো, ফস্কানোটা যেন অভ্যাস না হয়ে যায়।’ নিজের ব্যাপারে সিরিয়াস, অন্যের ব্যাপারেও। সিরিয়াস বলেই তো লিখতে রাজি হতো না। অথচ লেখাটাকে আমরা কেউ কেউ অভ্যাসে পরিণত করবার তালে ছিলাম। বুঝি না-বুঝি, হোক না-হোক লিখে ফেলি, পত্রিকাতে ছাপাই।
পড়তে যারা যায় বিলেতে তাদের অধিকাংশেরই অভীষ্ট থাকে পিএইচ ডি করবে। নামের আগে কোনোমতে ‘ডক্টর’ লিখতে পারলে আর বাকি থাকে কি? পাণ্ডিত্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ তখন অবান্তর এবং উন্নতির অনেক দ্বার অর্গলমুক্ত। আমরা সবাই গেছি পিএইচ ডি’র খোঁজে, কেবল গিয়াসই দেখলাম ভর্তি হয়েছে অনার্স কোর্সে। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্ থেকে বিএসসি অনার্স করবে আন্তর্জাতিক ইতিহাসে। বললো, গভীর ও ধারাবাহিকভাবে জানা চাই। তাকে টলায় কার সাধ্য।
সেই সময়ে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, আমি ও আমাদের অকালপ্রয়াত বন্ধু আবিদ হুসেন। আবিদের লন্ডনবাস তখন অনেক দিনের, সে-ই নিয়ে গেল গিয়াসের আবাসে, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে। ১৯৬৫ সালের কথা। গিয়াসকে নিয়ে আমরা বের হয়েছি হাঁটতে। দেখি লোকজন যেন তাকাচ্ছে তাঁর দিকে। তা তাকাবারই কথা। গিয়াস পরেছে সিল্কের পাঞ্জাবী-পাজামা, গায়ে চাপিয়েছে সাদা চাদর। একেবারে খাঁটি স্বদেশী মূর্তি।
পরে আবিদ বলেছে আমাকে, ‘দেখলে কাণ্ডখানা। এই শহরে আমরা চেষ্টা করি যত কম সম্ভব দৃশ্যমান হতে, সে জন্য ছদ্মবেশে থাকি। ওদের ধার-করা জামাকাপড় পরি। আর গিয়াস কেমনভাবে ঘোষণা করছে নিজেকে।’
গিয়াস কিন্তু মোটেই জানত না যে সে কোনো ঘোষণা জারি করছে। তাঁর ভাবটা এই রকমের যে, আমাদের নিজস্ব পোশাক আছে, সেটা পরব, তাতে তোমাদের কী বলার আছে? এমনই সাহসী এবং স্বকীয় ছিল সে। তাঁর দেশপ্রেম সে ঘোষণা করেনি কখনো। কিন্তু সে ব্যাপারে ছাড় দেয়নি এতটুকু। যে জন্যই তাঁকে প্রাণ দিতে হলো। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা পিছিয়ে ছিলাম তাঁর তুলনায়, সাহসের ক্ষেত্রেও।
পেছনে ফিরে মনে হয় গিয়াসউদ্দীন কেবল নিজেকে নয়, আমাদের জীবনেরও একাংশকে নিয়ে চলে গেছে সঙ্গে করে। একাত্তরে যাদের আমরা হারিয়েছি সে-হারানোর কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। গিয়াসের স্মৃতি দুঃখ জাগায়, ধিক্কারও জাগায় নিজের মধ্যে। ঘাতকেরা এখন উল্টো রাষ্ট্রক্ষমতার অংশ হয়ে গেছে। যতদিন না এর প্রতিকার হয় ততদিন কেবল যে দুঃখ থাকবে তা নয়, জেগে থাকবে অপরাধবোধও।
লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা/তারা//



































