কবি হুমায়ূন আহমেদ
মুম রহমান || রাইজিংবিডি.কম
প্রকাশিত: ০৯:০১, ১৩ নভেম্বর ২০১৬
আপডেট: ০৫:২২, ৩১ আগস্ট ২০২০
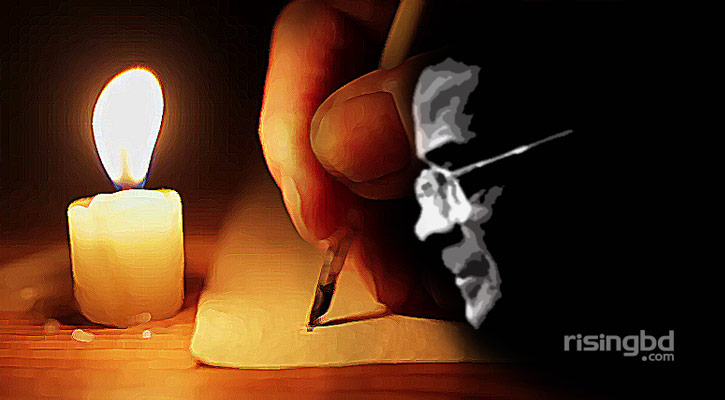
অলংকরণ : অপূর্ব খন্দকার
Ñ
ফাঁকি?’
সংগীত।’
Or else, the baby will cry for the soil’’
But those, tear won’t the irrigate
The arid earth of our lives?’’
রাইজিংবিডি.কম



































